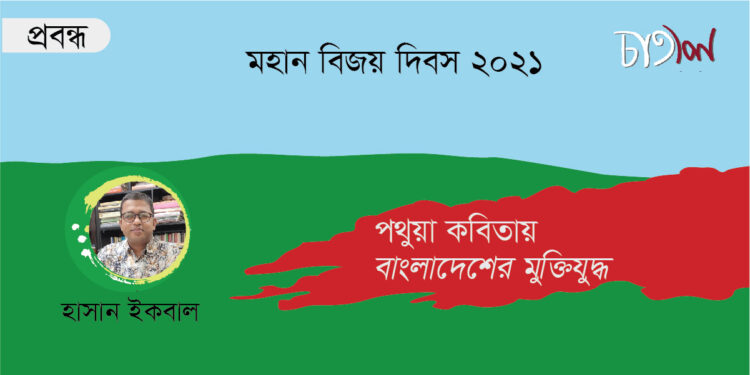[লেখাটি শুরুর আগে ছোট্ট একটি ভূমিকা টেনে নেওয়া জরুরি বলে আমি মনে করছি। লোকসংস্কৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি নানান আঙ্গিকে উঠে এসেছে। অঙ্গিকতার ভিন্ন ধারায় পথুয়া কবিতায় মুক্তিযুক্ত প্রসঙ্গটি বাদ যায়নি। মাসিক শব্দঘর পত্রিকায় ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় সে বিষয়ে আমার একটি প্রচ্ছদ রচনা ছাপা হয়েছিল ‘ভাটকবিতায় মুক্তিযুদ্ধ’ শিরোনামে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর অনেকেই সে ব্যাপারে অনেক গঠনমূলক মতামত দিয়েছিলেন। এর পরপরই আমার হাতে আসে ভাটকবিতা/পথুয়া কবিতা বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ/নিবন্ধ এবং বেশকিছু মূল ভাটকবিতা। পরিচিত হই জীবিত আছেন এমন কয়েকজন চারণ কবির সাথেও। সে বিষয়গুলো আমাকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে। এ পরিসরে নতুন করে ভাটকবিতা বা পথুয়া কবিতার প্রাক-পরিচয় তো থাকছেই, চেষ্টা করেছি নতুন কিছু তুলে ধরার, সাথে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটিও।]
এক.
সারাদেশ ডুবছে পানিতে-বন্যায়। স্কুল নেই–পড়া নেই। সারাদিন নৌকায় বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা। বিকেলবেলা দাদীর হাতে ভাজা চালের গুড়ো খাই–গাছের পেয়ারা, এটা সেটা। আমাদের কলতলা তখন ডুবো ডুবো। খাবার পানির অভাব শুরু হয়েছে। গ্রামে শুরু হয়েছে রোগশোকের প্রকোপ। বানের পানি কমতে শুরু করেছে। কিন্তু বাড়তে লাগলো স্কুলে যাবার টেনশন। সেই ছেলেবেলা– বয়স হাতে গুনে সাত কী আট হবে। বন্যায় স্কুলের ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে স্কুল ছুটি। পানি কমে গেছে-রাস্তা ঘাট শুকাতে শুকাতেই, মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেছে। আমরা বেড়াতে গেছি আত্মীয়ের বাড়িতে। রাতের বেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিছানার নিচে আবিষ্কার করলাম অদ্ভ–দ এক কাগজের বান্ডিল। শয়ে শয়ে নয়–হাজারে হাজার। অগুনতি। কোনটা দুমড়ানো-মুচড়ানো, কোনটা আনকোরা। আমার সচকিত জিজ্ঞাসা
―এইগুলো কী কাগজ?
―এইগুলো কাগজ না, কবিতা।
―কিসের কবিতা?
―নানান কিসিমের, নানা ঢংয়ের।
―একটা শোনান না!
―এইগুলো তুমরা বুঝবা না। তুমরা বালক ছেলে।
কবিতার সাথে পরিচয় ঘটেছিল আমার সেই বালক বয়সে। আমার চিনতে কষ্ট হতোনা এর পড়ার ছন্দের মধুময় সুর। এতশত কবিতা। ছেলেবেলায় এই স্মৃতিটুকু আমাকে বিমোহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙানোর পর যখন আবার ফিরে গেলাম সেই কবিতার খুঁজে–কবিতা খুঁজে পাইনি–সেই কবিতার মানুষগুলোও ততোদিন বেঁচে নেই। যারা ছিলেন তৃণমূল পর্যায়ের স্বভাব কবি।
বলছিলাম কবিতার কথা। এই কবিতা কখনো শিকুলি, কখনোবো সায়েরি। এই কবিতা অঞ্চলভেদে ভিন্ন নামে পরিচিত। কোন অঞ্চলে ভাটকবিতা, কোথাওবা পথুয়া কবিতা, আবার কোথাও কোথাও হাটুরে কবিতা নামেও প্রচলিত। পুঁথিকাব্য, পুঁথি কবিতা, পথের কবিতা, গ্রাম্য কবিতা এ নামগুলোও বেশ শোনা যায়। এসব কবিতা বাঙালি সমাজের অন্তর্গহীন সংস্কৃতিবোধের স্বতস্ফূর্ত এক আঙ্গিক। ভিন্নমাত্রার এসব কবিতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এরই প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের আগেও পরে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। চলচ্চিত্র, গান, নাটক, উপন্যাস ও কবিতায় যেমন উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা, তেমনি যুদ্ধদিনের ছবি এঁকে ছিলেন আমাদের গ্রাম্য কবিরা তাদের পথুয়া কবিতায়। সে সময়ের পথুয়া কবিতায় জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার।
পথুয়া কবিতা। এ কবিতার সন্ধান মেলে নানান জায়গায়, নানান অনুষঙ্গে। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত এক শ্রেণির কবি কোন বিশেষ ঘটনা বা বাহিনীকে উপজীব্য করে তার কল্পনার জগৎ প্রসারের মধ্য দিয়ে অনেকটা গীতিকবিতার আদলে ও পয়ার ছন্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকবিতা রচনা করেন। পরে তারা বিভিন্ন হাটবাজার, লঞ্চ-ষ্টিমার, ট্রেন, বাস বা কোনো জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে অনেকটা পুঁথি পড়ার মতো সুর করে পড়েন। এভাবে ঘুরে ঘুরে আসর জমিয়ে ভাট কবিতা, পথুয়া কবিতা, হাটুরে কবিতা বিক্রি করেন কবি বা বিক্রেতারা। এ কবিতার প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই দেখা যায়। মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীর চৈত্র ১৩৩৫ সংখ্যায় ‘বঙ্গভাষার উপর মুসলমানদের প্রভাব’ শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেন–
‘বঙ্গভাষা বঙ্গের পল্লীতে মুসলমানদের কিরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা পূর্ববঙ্গের শত শত ছোট মুসলমানী কবিতা গানে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অতি অল্প আয়াকে ১৮৮ খানি সেইরূপ মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই মুসলমানের লেখা। স্থানীয় এমন কোন ঘটনা নাই, যাহাদের সম্বন্ধে কৃষক কবিগণ পালাগান রচনা না করিয়াছেন। আরও শত শত পুস্তক ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৎসর বৎসর এই ভাবের বহু সংখ্যক পুস্তিকা রচিত হইতেছে। মুসলমানদিগের ঐতিহাসিক বৃদ্ধি ও রুচি স্বত:সিদ্ধ। এমন কোন ক্ষুদ্র কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা নাই, যাহা পল্লী কৃষকের দৃষ্টি এড়াইয়াছে। তাহারা বঙ্গদেশে যখন যা ঘটিয়াছে তখনই সে সম্বন্ধে পালাতান রচনা করিয়া তাহা স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, নৌকাডুবি, যাহা কিছু হয়, মুসলমান কৃষক তখনই তাহা লইয়া বাঙ্গলীয় পালাগান রচনা করিয়া থাকে।
…এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার কামাল পাশা, ব্রহ্মদেশের লড়াই থিবোর কথা ও মনিপুরের যুদ্ধ হইতে সামান্য মাঝির নৌকাডুবির বৃত্তান্ত পর্যন্ত সকল কথাই কবিতার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তিকা পাড়া গাঁয়ের খবরের কাগজের কাজ করিয়া থাকে। উহা দ্বারা এই কথা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালভাষা পল্লীর নিরক্ষর মুসলমানদের হাতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।’
পথের কবিতা নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত অনেক আগেই ছিল! তবে বিদ্ধৎসমাজেও এ নিয়ে ভিন্ন নাম শোনা যায়। তাদের লেখালেখিÑগবেষণায় এ পার্থক্যগুলো ধরা পড়ে। শামসুজ্জামান খান ও মোমেন চৌধুরী এ কবিতাকে বলেছেন ‘পথুয়া কবিতা’। অধ্যাপক আহাম্মদও এ কবিতাকে বলেছেন ‘পথুয়া কবিতা’। ৩ আতোয়ার রহমান বলেছেন-‘পথের সাহিত্য’। আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন ‘ভট্ট সঙ্গীত’।
দুই.
পথের কবিতা জিনিসটা কী? এই কবিতা কী সবাই পথে বসে লিখে? কবিতার জন্ম হয়–এখানে সেখানে, গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে। এই কবিতার সর্বগ্রাসী বিস্তার আকুল করেছিল সরলমনা মানুষের মন প্রাণ। এই কবিতার শক্তি অকল্পনীয়, কবিতার জন্ম হয়েছিল অনেকদিন আগে। লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা এটি। কোথাও কোথাও বলে ভাট কবিতা বা ভট্ট সঙ্গীত। বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে ‘শিকুলি’। ঢাকা ও ময়মনসিংহে ‘কবিতা’ নামে পরিচিত। বরিশালে ‘পুথি কবিতা’ এবং সিলেট অঞ্চলে ‘কবি’ আবার কোথাও সায়েরি নামেও বলা হয়ে থাকে। মূলত: পথের কবিতা পথুরা কবিতা এক ধরনের কবিতা। গবেষক লেখকরা যাই বলে পরিচিতি করান না কেন এ বিষয়বস্তু একই। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বাদশভাগে ১৩১২ সংখ্যায় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য ভাটকবিতা কিংবা পথুয়া কবিতাকে বলেছেন-‘গ্রাম্য কবিতা’।
অধ্যক্ষ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৮-১৯৩৮) সিলেট অঞ্চলে ভট্টপদবী ধারী জনগোষ্ঠীর অনেকে লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে মৌখিক কবিতা রচনা করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সুর করে তা জনসমক্ষে প্রচার করতেন। এই কবিতাকে ভট্টকবিতা বা ভট্টসঙ্গীত বলা হতো। এই ধরেনের পথ কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত এবং ফরমায়েসী- দু ধরনেরই লেখা হতো। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও এ কবিতা এখন খুব একটা দেখা যায় না।
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সিলেটের বানিয়াচঙ্গয়ের দুজন লোককবির ভট্টকবিতা সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ১৯৩৬ সালে ভট্ট কবিতা সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পদ্মনাথ তার সংগৃহীত ভট্টকবিতা এবং ভট্ট কবিদের জীবনী শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে জমা দেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ তিনি শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে শ্রীহট্টের ভট্টকবিতা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি সাইত্রিশটি ভট্টকবিতা সংগ্রহ করেছিলেন।
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ) ১৩৪৪) ‘ভট্ট কবিতা সংগ্রহ’ প্রবন্ধে পদ্মনাথ ভট্টচার্য ভট্ট কবিতা সংগ্রহের কাহিনীর সঙ্গে এই কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি লিখেছেন-
‘ভট্ট কবিদের দ্বারা নানা প্রকারের লোকশিক্ষার প্রচার হয়।…ইহাদের কবিতার বিষয় কেবল প্রাচীন উপাখ্যানই নিবদ্ধ নহে। কোনরূপ অভিনব ঘটনায় সমাজে আন্দোলন আলোচনার তরঙ্গ উঠিলে তাহাও ভট্টকবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।…কোনও দানশীল ধর্মপরায়ণ ভূস্বামী কোনও ধর্মানুষ্ঠান করিলে ভট্টগণ তাহার যশোগীতি প্রস্তুত করিয়া সমাজের সর্বত্র সদুনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে অপর ধনীরাও সংকার্য্যে প্ররোচিত হইতেন। দেশে যখন খবরের কাজগ ছিল না। ভট্টগণ ঐ রূপে নানা ঘটনার সাধারন্যে প্রচারের কাজ করিয়াছেন।’
ভট্টকাব্য/ভাটকবিতা/পথুয়া কবিতা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ‘ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান’ শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। ধারাবাহিকভাবে এ লেখাটা প্রকাশিত হয় ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৬), ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ ১৩৪৬), ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪৭), এবং ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৪৯)। মুসলমান ভট্টকবিদের রচনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ভট্টকবিতা সম্পর্কে তার প্রবন্ধে লিখেছেন–
‘ভট্ট কবিতা রচনায় ভাট কবিগণ এতই অভ্যস্থ যে তাঁহারা যে কোন স্থানে বসিয়া যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া সহসা কবিতা রচনা করিতে পারেন। ভাটের কবিতা একই নির্দিষ্ট সুরে গীত হইয়া থাকে। ইহা অতি শ্রুতিমুধর। সাধারণ সমাজে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া এই শ্রেণির কবিতা গাহিয়া অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই ভাট কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানেও এই শ্রেণির অনেক কবি পল্লীগ্রামগুলোতে রহিয়াছেন।’
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউসুফ জুলেখা, রসুল বিজয় লাইলী মজনু, মধু মালতী, ওফাৎ-ই-রসুল, পদ্মবতী, হাতেম তাই, ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান, সোনাবান ইত্যাদি পুঁথি সাহিত্যে যেমন তার আপন সত্ত¡া ও মহিমা প্রকাশ করে গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে ঠাঁই করে নিয়েছিল, ভাটকবিতাও সেভাবে স্থান করে নিয়েছিল মানুষের মনে। আতোয়ার রহমান ‘পথের সাহিত্য’ শিরোনামে একটি দারুন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সে প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি––
‘একসময় এ কবিতা প্রায়ই দেখা যেতো। পৃষ্টা কয়েকের একখানি পুস্তিকাগুলো ধরে দুই তিনজন মিলে সুর করে কাহিনীমূলক ছন্দিত রচনা শোনাতো। শহরের কোনো রাজপথের মোড়ে এবং জন চলাচলের কয়েকটি জায়গায়। এখন তারা দুর্লভ। …পুরনো পুস্তিকাও এখন আর বড়ো একটা মেলে না। এদিকে ছন্দিত রচনাগুলির সুরাশ্রয়ী আবৃত্তি বা গীতাকার পরিবেশনের সাহায্যে ভীড় জমিয়ে পুস্তিকা বিক্রি করে যা পাওয়া যেতো, তার স্বাধীনতা পূর্বকালীন পরিমান যেমনি হোক না কেন, বর্তমান পরিমান আদৌ-আকর্ষণীয় নয়। …এই পুস্তিকাগুলি একদা আমাদের শহর-গঞ্জের এবং গ্রামের প্রাকৃতমনের চিত্তবিনোদনের একটি উল্লেখযোগ্য অবলম্বন ছিলো। এখন সে অবলম্বন কার্যত অবলুপ্ত। এবং প্রাকৃতজন তার কোনো বিকল্পও যায়নি। ….রাজধানীতে যারা পুস্তিকাগুলির কাহিনী সুর করে শুনিয়ে বেড়াতো, তারা সেগুলির রচক নয়, বিক্রেতা। রচকরা-দুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া প্রাকৃতজন এবং থাকেন সাধারণত গ্রামাঞ্চলে। যেমন তাদের পাঠকজনও।…পুস্তকগুলি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের উদ্যোগও নেই। তার ফলে এগুলি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এদিকে পুস্তিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে অধিকাংশ মফস্বল থেকে। প্রায়ই ছোটো ছোটো ব্যাবসায়ীর মাধ্যমে। যারা রচকদের সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে স্বত্ব কিনে নেন এবং খুচরো আর পাইকারী বিক্রীর ব্যবস্থা করেন।’
আতোয়ার রহমান মনে করেন যে, কবিতাগুলির ভাষা ও রচনাশৈলী ইত্যাদিতে এমন কিছু নেই, যা মার্জিত রুচি সাহিত্য পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলি সম্পর্কে তাদের তাই কৌতুহলে দেখা যায় কদাচিৎ। এ জন্য এ রচনাগুলি অনালোচিত রয়ে গেছে। গ্রামের অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর কবিরা কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতি-দুর্যোগ, প্রেম বা কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় ইত্যাদি নিয়ে সহজ ভাষায় লিখিত কবিতা যেগুলোর শ্রোতা সমঝদার গ্রামের অর্ধশিক্ষিত ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর জনগণ। সে কবিরা রচনা করেছিলেন দেশপ্রেমের উদ্দীপনামূলক কবিতা, গণজাগরণ, স্বদেশী আন্দোলন, বাংলাদেশের সংগ্রাম, এসব বিষয়েও।
মূলত উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এসব ভাটকবিতা, পথুয়া কবিতা মুদ্রিত হতে থাকে। এসব কবিতা ক্রাউন বা ডাবল ডিমাই সাইজের কাগজে মুদ্রিত। অধিকাংশই নিউজ প্রিন্ট বা নিম্নমানের কাগজে সেলাই বাঁধাহীন ভাঁজ করা কাগজ। এগুলো অধিকাংশই আট পৃষ্টার তবে বারো বা ষোল পৃষ্ঠার কবিতাও দেখা যায়।
তবে পুস্তিকাগুলোর অধিকার্ংশ ১৭দ্ধ১১ সে.মি. এছাড়া কোন কোনটি ১৮দ্ধ১১ সে.মি., ১৮দ্ধ১২ সে.মি, ১৯দ্ধ১৩ সে.মি. আয়তনও দেখা যায়। পুস্তিকাগুলোর উপরিভাগে আল্লাহ আকবার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ইত্যাদি স্তুতিবাচক শব্দ। এর নিচে শিরোনাম ও কবির নাম ঠিকানা। কবিগণ তাদের নামের আদ্যে স্বঘোষিত উদাস কবি, কবি সম্রাট, কবিরত্ন,, চারণ কবি ইত্যাদি অভিধা ব্যবহার করেছেন। পুস্তিকাগুলির প্রথম অর্থাৎ প্রচ্ছদপৃষ্ঠা প্রায় ক্ষেত্রেই বিচিত্র। অধিকাংশ পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার শীর্ষভাগ ‘এলাহি ভরসা, ‘হুয়াল গনি ভরসা’ লেখা থাকতো।
আসাদ চৌধুরীর লেখা ‘ভিন্ন ধরনের কবিতা প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধে কবিতার ধরনের ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। পথুয়া কবিতা কিংবা ভাটকাবিতাকে কবিতাই বলেন কবিরা। এসব কবিতা পড়েন খুব কম লোকই, তবে শুনেন অনেক মানুষ। কবিতার বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের ও ভূমিকা যাতে নামকরণে যেমন- প্রেমের কবিতা, খুনের কবিতা, টেডী কবিতা, স্বদেশী আন্দোলন কবিতা, গনজাগরণ কবিতা।
ভাটকবিতা কিংবা পথুয়া কবিতার কয়েকটি প্রচ্ছদ চিত্রের বিরবণ তুলে ধরলে পুরো অবয়বটি সহজে দৃশ্যমান হবে বলে আমি মনে করি। হিরা মিঞার ‘আলমচান্দের দুঃখের কথা’ কবিতায় রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ, কে গনি কলম্বীর ‘সন ১৩৬১ বাংলা ভয়াবহ ধ্বংসলীলা’ কবিতার পানির উপর ভাসমান নৌকা। আব্দুল করিম খান এর ‘নারীর আচরণ’ এর প্রচ্ছদে ধানভর্তি কুলো হাতে গৃহবুধু। আব্দুল করিম এর ‘হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের যুদ্ধ’ পুস্তিকার শিরোনামে উপরে বন্দুকের ছবি, আব্দুর রাজাক মিঞার ‘ছায়াদেবীর প্রেমকাহিনীতে’ মালা হাতে ডানা ওয়ালা উড়ন্ত পরী। জালাল খান ইউসুকীর লেখা ‘খোদার গজব’ কবিতার প্রচ্ছদে মসজিদের পাশে ভূগর্ভে প্রোথিত লোককে চারজনে ওপরে টেনে তোলার দৃশ্য। এইসব পুস্তিকায় প্রচ্ছদ চিত্রের ব্যবহার বিশ শতকের পঞ্চাশ এর দশকের আগে তেমন দেখা যায় না। প্রচ্ছদ চিত্রের নিচে কোন ঔষধের বিজ্ঞপ্তি, অত্র কবিতা নকলকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি, মামলা, ক্ষতিপূরণ, জেলজুলুমের ভয় অথবা ‘আল্লাহর কাছে দায়ী থাকিবেন’ ইত্যাদি বক্তব্য দেয়া হয়েছে। কবিতার শুরুতে বন্দনা, প্রায় কবিই মাত্র এক পঙ্ক্তিতে বন্দনা সমাপ্ত করেছেন। কোনটি দুচার বা ততোধিক পঙ্ক্তির। কবিতা শুরুর আগে ‘কবিতা শুরু’ বড় অক্ষরে লেখা থাকে। কোন কবিতাতে লেখা থাকে ‘বন্দনা’ ।
তরতাজা ঘটনা নিয়ে শিক্ষিতজনের শিক্ষিত কবিরা সবসময় বড় একটা লেখেন না। কিন্তু এই কবিদের বৈশিষ্ট্যই হলো সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে লেখা। যেসব লেখায় সত্য থাকবে এমন দাবী শ্রোতার করেন না, তবে থাকলে খুশী হন। কবিতার কাটতি বাড়ে, পাইকাররা দুই ডজন, তিন ডজন কিনে নেনÑকখনো শয়ে শয়ে। দাঁতের মাজন, মলম, তাবিজ ও গাছ গাছালি হইতে দেশীয় মতে প্রস্তুত অষুধ-বিষুদ বিক্রেতারাই এসব কবিতার প্রধান যোগানদার। কোনো কোনো কবিতা এতই জনপ্রিয়তা পায় যে, নকলেরও ভয় থাকে। আতঙ্কিত কবি আইনের ভয় দেখান, ধর্মেরও দোহাই দেন এবং তা যথারীতি প্রথম পাতাতেই-
‘আমার এই কবিতা আমার অনুমতি ছাড়া কেহ ছাপিলে ও নকল করিলে আইন আমলে আসিবে ও তাহার জীবনে যত নেকী করিয়াছে তাহা আমার কাছে বিক্রয় হইবে ও কেয়ামত পর্যন্ত দায়ী থাকিবে।’
(ক্লাশের বন্ধু ও দুঃখিনী ছেলের কবিতা)
কখনো এমন লেখাও চোখে পড়ে কবিতার পাতায় সতর্কবাণীতে-
‘যিনি এই কবিতা নকল করিয়া ছাপাইবেন সরকারের আইন অনুযায়ী বিশ হাজার কবিতার পাইকারী হরে জরিমানা দিতে হইবে। আমার এই ক্ষুদ্র কবিতাখানি নকল করিয়া মাতাপিতাকে গালি শোনাইবেন না। আরও মনে রাখবেন চোরের বাড়িতে ছালাম ওঠে না।’
আরো বলে দেয়া হয় যে-
‘পাইকারী হারে বিশ হাজার কপির হিসাবটা ‘যারা নকল করিয়া ছাপাইবেন’ তারাই করুন-কিন্তু খুচরা দাম পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। তবে সঙ্গে যদি আরো ‘কবিতা’ কেনেন সস্তায় পাবেন।’
এখানে পথুয়া কবিতার বন্দনা অংশের কিছু নমুনা তুলে ধরছি। যা থেকে সহজেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে।
বন্দনা:
লইয়া আল্লার নাম/বসিলাম/কলম নিয়া হাতে
হারিকেন জ্বালাইয়া/একটা/গভীর রজনীতে/ মনে জাগিল।
আব্দুল করিম খান রচিত একটি পথুয়া কবিতার বন্দনা অংশ এরকমÑ
আমি প্রথমে বন্দনা করি নামেতে আল্লার
তার পরে বন্দনা করি নবী মুস্তফার।
তারপরে বন্দনা করি ওস্তাদের পায়
তারপরে বন্দনা করি শ্রোতা বন্ধুগণে
যে আমার করুণ কাহিনী মন লাগাইয়া শোনে।
এ পর্যন্ত করি ক্ষান্ত সবার বন্দনা
এমন গাইব কবিতার সুরে কিচ্ছার বর্ণনা।
কোনো কোনো কবিতার শেষে ভনিতা আকারে বইয়ের দাম, লেখকের নাম ও ঠিকানা জুড়ে দেয়া হয়–এছাড়া বইয়ের পাতায় ওস্তাদের নাম ও লিপিবদ্ধ থাকে-
এই পর্যন্ত ইতি করি প্রেমের কাহিনী
পাইকারীতে সস্তা আট আনা একখানি।
নামটি আমার নুরুল ইসলাম সভায় প্রকাশ করি
পোস্ট অফিস নবাব গঞ্জেতে ঢাকার জেলায় বাড়ী।
সালাম জানাই ওস্তাদের পায়
ওস্তাদ আমার করিম খান।
পথুয়া কবিতা/ভাটকবিতাগুলো যদিও কবিতা, তবু এগুলো কবিতার মতো গুরুগম্ভীর স্বরে পঠিত হয়না। এগুলো একটি স্বতন্ত্র সুরের মাধ্যমে পঠিত হয় যা ফোকলোরের অন্যান্য সঙ্গীতের মধ্যে দুর্লভ ফলে ভাটকবিতা ফোকলোরের একটি আলাদা দিক উন্মোচন করছে এর সুর দ্বারাও একটি পৃথক জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সুরের বৈচিত্র বেশি না থাকলেও মাঝে মাঝে ধুয়া ও অন্যান্য সুর পরিলক্ষিত হয়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই অধিকাংশ কবিতা রচিত। সুরাশ্রয়ে কবিতাগুলো পঠনের স্টাইল শ্রোতাকে সহজেই আকর্ষণ করে। যেমন-
‘প্রথম আল্লা নবী ই মনে ভাবি কলম নিলাম হাতে
কবিতা লিখিতে বাসনা হইল মনেতে। পরে লিখে যাই।’
কবিতার শুরু থেকে প্রতি বেজোড় সংখ্যক পংক্তির তিন মাত্রাবৃত্তের প্রথম পদটি দুবার পঠিত হয় যার ফলে এটি একটি ভিন্ন মাত্রা পায় এবং বক্তব্যটি একটি আকর্ষণীয় ধ্বনিব্যঞ্চনায় শ্রোতাকে মোহবিষ্ট করে তোলে। খুব সম্ভবত দিত্ব উচ্চারণের এই রীতিটি মধ্যযুগের পুথি থেকে অনুসৃত। এই কবিরা শুধুমাত্র একঘেয়ে প্রেমকাহিনি বর্ণনার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারা বিচিত্রধর্মী বিষয়াদি নিয়ে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রেমকাহিনিমূলক কবিতায় যেমন রগরগে বর্ণনা রয়েছে তেমনি ভাষা ও শব্দচয়নেও যৌনগন্ধি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যেমন- শিউলী বাদলের প্রেমের খেলা, গৌরীবালা ও সুবোধের মধুর মিলন কবিতা, বউ বদলের কবিতা, সাহেদ আলী ও জরিনার হালকা প্রেমের কবিতা, কবিতা রসের ভান্ডার, বজলু মিয়া ও কমলা সুন্দরীর কবিতা, রিক্সাওয়ালা জলিল মিয়া ও ফুলমালার প্রেমের কবিতা, পদ্মার গাঙে প্রেমের খেলা কবিতা, হক ও লতার প্রেমের কবিতা। লিপিরানী ও আনোয়ারের প্রেমের কবিতা, নোয়ার আলী ও প্রিয় বালার প্রেমের কবিতা, বকুল মিয়া ও চান মিয়ার পীরিতের তুফান কবিতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অসম প্রেমের সম্পর্ক বিষয়ক অনেক কবিতা রচিত হয়েছে, যেগুলোর শিরোনাম দেখলেই সহজে অনুমেয়। যেমন– লাং ধইরাছে স্ত্রী তাই– স্বামী করছে স্ত্রী জবাই, নাতী করে দাদী বিয়া-দশ লাখ টাকা মহর দিয়া, বেতিন গাঁয়ের গফুর হাজী – ভ্যাস্তাবউকে করছে রাজী, চাচা-ভাস্তির প্রেম-কাহিনী কবিতা, শ্যালীদের প্রেমে দুলাভাই- সাত বোনের এক জামাই, খালা বোনপুতের প্রেম কাহিনী, শ্বাশুড়ীর প্রেমে জামাই খুন, মামা শ্বশুড় ও ভাগ্না বউয়ের কবিতা, শোনেন আমার পাঠকগণ–বউ কাটিছে স্বামীর ধুন, খোদার গজব দারুন কড়া–জামাই শ্বাশুড়ী লাগছে জোড়া এ ধরনের কবিতা উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলো প্রাচীনকাল থেকে রচিত হয়ে লোকমুখে চলে আসছে। এর প্রচলন কখন শুরু হয়েছিল তার সঠিক কাল এখনো নিরূপিত হয়নি। মুদ্রিত আকারে এ ধরনের কবিতার প্রচার- প্রসার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। মুন্সি আবদুর রহমান প্রণীত ‘১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষের পুঁথি’ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ‘আকালের পুঁথি’ এবং একই বৎসরে মুদ্রিত ‘তিরিক্ষা জ্বরের পুঁথি’ ওয়াইজদ্দিন-এর ‘গরকির বচন’ ১৮৭৬ সালের ঘুর্নিঝড়ের ওপর ভিত্তি করে কোরবান উল−াহর ‘খন্ড প্রলয়’ (১৮৭৭) প্রভৃতি মুদ্রিত আকারে ভাটকবিতার প্রাচীন নমুনা। বিশ শতকে বাংলাদেশে অসংখ্য ভাটকবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এগুলো আনন্দ- উত্তেজনার বিষয় হিসেবে সমকালে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে সে সব হারিয়ে যায়। মুদ্রিত ভাটকবিতাগুলো ‘একমাত্র ব্যবহারের সামগ্রী’ হওয়ায় কেউই এগুলো সযতেœ রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেননি।
(তিন)
পথুয়া কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণমুক্তি আন্দোলন, কিংবা স্বাধীকার আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এসব বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে অনেক পথুয়া কবিতা রচিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধ সময়কালীন, যুদ্ধের আগেও পরে। সহজ ভাষায় রচিত কবিদের অনেকেই বেঁচে নেই। তবে এ বিষয়ে তথ্য ও লেখা সংগ্রহের তাগিদে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে আমাকে। বেঁচে আছেন-এখনও কবিতার চর্চা করেন সে রকম কবির সাথেও আমার পরিচয় হয়েছে। এ পরিসরে কয়েকজন কবির নাম বলা যেতে পারে। যারা বেঁচে আছেন। ময়মনসিংহের বাউল কবি ফজলু মিয়া, কবি আব্দুর রশিদ সরকার। ‘নারী ও পুরুষের শিক্ষা’ কবিতার জন্য তারা বিখ্যাত। কবি আবু বকর সিদ্দিক তিনিও একজন ভাটকবি। কিন্তু এ পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। ট্রেনে ঘুরে ঘুরে তিনি এখন নানান জিনিস বিক্রয় করেন। পরিচয় পর্বের এক পর্যায়ে তার থলের নীচ থেকে বের করে দেন বেশ কিছু কবিতা সংগ্রহ। জীবিত পুঁথিকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে জালাল খান ইউসুফী একটি পরিচিত নাম। তার জন্ম সিলেটের ওসমানী নগরে। তার বাবা পুঁথিকবি প্রয়াত হাকীম ইউসুফ ছিলেন লোকসাহিত্যের কিংবদন্তী এক পুরুষ। জালাল খান ইউসুফীর কবিতাগুলো রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর। তিনি ভাটকবিতাকে/পথুয়া কবিতাকে বলেছেন-‘পুঁথিকাব্য’।
এই পুঁথিকাব্যকে কেউ কেউ আবার ‘বটতলার কবিতা’ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। পুঁথিকাব্যের কবি ও মধ্যযুগের পুঁথিকারদের মেধা দক্ষতার বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই এ কবিরাই শীর্ষ মেধাবী। এ ধারার কবিরাই পনেরটি সুরের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। শুধু তাই নয়-তারা স্মৃতি থেকেও গাইতেন অনর্গল তিন-চার পাতা, আধা ফর্মা, এক ফর্মার কবিতা। ‘পথ-কবিতা’ নিয়ে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন যে-
‘…ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় ‘চারপেজি, আটপেজি বা ষোলোপেজি ডাবল ডিমাই আকারের নিউজপ্রিন্টে নিম্নমানের প্রেসে ছাপা’ চটি বই বিক্রি হতো। ওই শতকে রচিত বেশির ভাগ পথ-কবিতারই বিষয়বস্তু ছিল ১৮৯৭ সালের ঢাকার ভূমিকম্প এবং ১৮৮৮ সালের টর্নেডো।
…কিছু কিছু পথ-কবিতা রচিত হয়েছে ‘অশ্লীল’ বিষয় নিয়ে, কিছু কিছু হিন্দুদের উৎসব নিয়ে। ওই সব পথ-কবিতা সমসাময়িক ঘটনার ও বিষয়ের ‘বিশ্বস্ত দলিল’ এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্রমোন্নতির কারণে এসব প্রকাশনা স্তিমিত হয়ে আসে।’
১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বরাজের ধ্বনি উত্থিত হয়। ভারতবর্ষের চরমপ›হী নেতারা বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বদেশীরা আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের অনুকরণে একটি অভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃটিশ পণ্য বর্জন, বিদেশী নীতি ও আদর্শ পরিহার করার নীতি গ্রহণ করেন। পাশাপাশি দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার ও স্বদেশী আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ হতে জনগণকে আহবান জানান। নেতাদের মতো পাড়াগাঁয়ের লোককবিরাও কবিতার মাধ্যমে জনগণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ভাটকবি জোনাব আলীর লেখা ‘স্বদেশী আন্দোলন’ কবিতাটি এই পরিসরে তুলে ধরা যুক্তিসঙ্গত বলে করি। স্বদেশী আন্দোলনের পর আমরা অনেকগুলো সময় পার করেছি স্বাধীনতার সুবর্ণ কীরিট ফিরে পেতে। বেনিয়া বৃটিশ আমাদের আষ্টপৃষ্টে রেখেছিল নি®েপষণের যাঁতাকলে। ১৯৪৭এর দেশভাগের পর ১৯৫২এর ভাষান্দোলন খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু বাঙালির জনজীবনে এক একটা মূহুর্ত ছিল যুগযুগান্তরের মতো। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর সত্তরের নির্বাচন। তারপর ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর যে জীবনযুদ্ধ চলেছিল তা অবর্ণনীয় দু:খকষ্টে ভরা। বাঙালী জাতি সে অব¯হা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে মুক্তির আস্বাদ নিয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে। কবিতাটি এই-
অধম জোনাব আলী কয় দু:খের কথা বলে যাই-
ওরে ছালাম রাখি দশের পায়, গান্ধি নামে জয় দিয়াছে জাগায় জাগায়।
ও দিয়াছে গান্ধি নামের ধ্বনি, রাজ্য ছেড়ে উইঠা গেল মহারানী।
সে যে ছয় দফারও নারী আর পরবনা বিলাতীর ঐ শাড়ী
দেশী সদাই করব মোরা, খাবনা লবণ আর বিলাতী।
গান্ধি রাজার বাড়ী ছিল র‚পদেশে, বিলাত আইল কি হেকমতে।
ঢাকা শহর দিল্লীনগর বেড়ায় ঘুরে, ও শূন্যের উপর চালায় সাধের গাড়ী।
টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ জামালপুর আর সরিষাবাড়ী
স্কুলের ছাত্র হাজার চারি তুইলা দিল আদালত ফৌজদারী,
নীল পাগড়ি তুইলা দিল, দৌড়াইল চকিদারী পঞ্চাদি।
ওরে আরেকটি কথা শুনে আমার প্রাণও যায়-
ওরে টেলিগ্রাফে খবর পাই, মক্কা ঘরের চান্দা পুইড়াছে হায় মরি হায়।
ঐ ইংরাজ এ কাজ কেন করল, আজগুবি এক গান্ধি রাজা উদয় হল।
মুখে আল্লা রসুল বল, হিন্দু মুসলিম কমিটি করিল।
মুহাম্মদ আলী শওকত আলী, ওমর কয় চানমিয়া তার সেনাপতি ছিল,
হাজার হাজার সৈন্য টার সাথে, তার ঠেলায় সংসার কাঁপে।
কাটাকাটি লাইগা গেল ইংরাজের সাথে
ও ইংরাজের যত সৈন্য ছিল, রেলধুমা সব ফালাইয়া পালাই গেল।
মুখে আল্লা রসুল বল, হাজার হাজার সেনাপতি ছিল
সেনাপতির নাম কহিতে ভাই আমার লেখার দরকার হল।
ইংরাজ কয় ভারতবর্ষে কাপড় দিবনা, এমন রাজ্য রাখব না
কাপড়ের কল তুইলা দিব- আর দিব না।
গান্ধি কয় ভাবনা কিছু করি, চরকা কিনা দিব বাড়ী বাড়ী।
সূতা কাটবে যত নারী চরকা ঘুরবে বলিহারি।
সূতা কাইটা বুনাইয়া নেব ভাইরে নানান রঙ্গের শাড়ী।
[স্বদেশী আন্দোলন/ জোনাব আলী]
ভাটকবি হাছেন আলী। তিনি হাছেন আলী সরকার নামে লোকসমাজে বেশি পরিচিত ছিলেন। তার জন্ম নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার লাখপুর গ্রামে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ২০০৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুরবন করেন। পিতার নাম আয়নব আলী। তিনি নিজগ্রামের হাইস্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তার রচিত বিকৃত যৌনাচার ভিত্তিক ‘সাহাজ উদ্দিন ও কেরামতের প্রেমকাহিনী কবিতা’ ১৯৫৭ সালে ছাপা হয়েছিল। তার রচনায় রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনে দুটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ দুটি ঘটনা এই লোককবির মানসে কী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তার নিদর্শন স্বরূপ দুটি কবিতা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ খান পাঠান এর ‘বাংলাদেশের ভাট কবি ও কবিতা’ বই থেকে সংযোজন করা হলো।
কোন (অ) রাষ্ট্রে শুনিনারে ভাই এমন গন্ডগোল
বাংলা ভাষা ধ্বংস হল আমাদের আর থাকবে কি মূল!
কায়েদে আজম কৌশল করে বাংলাদেশ দিল পাকিস্তান করে
মেনে নিয়ে বাংলাভাষী করছিরে ভাই মহাভুল।
কোন (অ) রাষ্ট্রে শুনিনারে ভাই এমন গন্ডগোল।
জিন্নাহ সাহেব প্রেসিডেন্ট হয়ে এদেশে দালালী করে
বাংলা ভাষা ধ্বংস করে উর্দু ভাষা করল মূল।
কোন (অ) রাষ্ট্রে শুনিনারে ভাই এমন গন্ডগোল
শেখ মুজিবর প্রতিবাদ করে ¯হান পেল কারাগারে
ছাত্রদলে উদ্ধার করতে তারে হইয়াছে আকুল।
কোন (অ) রাষ্ট্রে শুনিনারে ভাই এমন গন্ডগোল
ভাবিয়া হাসানে বলে কইব কথা কোন কৌশলে
অধিক কিছু বলতে গেলে জেলখানা মোর হবে কুল।
কোন (অ) রাষ্ট্রে শুনিনারে ভাই এমন গন্ডগোল
[রাষ্ট্রভাষা/ হাছেন আলী সরকার]
হাছেন আলী সরকার-এর লেখা আরেকটি কবিতা হলো ‘জয় বাংলা’। সেই সময়ে জয় বাংলা ছিল মানুষের প্রাণের শ্লোগান।
জয় বাংলা জয় বাংলা বলে উড়াব আজ ন্যায় নিশান
হব না আর নত মোরা গাইব এবার স্বাধীন গান।
সত্যের বাণী তুলব ধরে যা হয় তা হবে পরে
থাকব না আর অন্ধকারে নাম খলাতে পাকিস্তান।
কাহন সেনাদের অত্যাচারে হল বাংলা ছারখার
রুখব এবার সবাই মিলে থাকবনা আর কারাগার।
বাংলা মায়ের সন্তান মোরা জাগিব এবার
পাদাঘাতে সরাইব খুনি ইয়াহিয়া স্বৈরাচার।
খ্রীস্টান বৌদ্ধ মোদের সাথী নাহি কভু হীন।
চার ভাইয়ে মিলিত হয়ে তুলব বজ্র-হুংকার
করব ধ্বংস কাহন সেনাদের জুলুম অত্যাচার।
সাজব আজি রণ-সাজে হব যোদ্ধা বীর
ন্যায়ের তরে ধরব অস্ত্র উঁচু করি শির।
[জয় বাংলা/ হাছেন আলী সরকার]
মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছু কবিতা রচিত হয়েছিল নানান বিষয় নিয়ে। বায়ান্নোর ভাষান্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডও পথুয়া কবিতায় উঠে এসেছে। এ প্রবন্ধে লোককবি, পুঁথিসম্রাট খ্যাত জালাল খান ইউসুফী রচিত কিছু কবিতা তুলে ধরব। যে কবিতাগুলো পুরনো কবিতার আদলে, ছন্দে লেখা হয়েছে।
শোনরে ভাই ভগ্নিগণে উনিশ’শ বায়ান্ন সনে
কি ঘটে যায় তৎকালিন বাংলায়
সেই ঘটনার কিছু কথা প্রকাশ করি কবিতায়
একুশে ফেব্রæয়ারি কোনো ইতিহাসের পাতায় জায়গা পায়।
ভারত কেন ভাগ হইয়াছে কিংবদন্তি স্বাক্ষী আছে
পাকিস্তান দেশ কেন জন্ম লয়
কেন আবার বাঙালিদের ভূখন্ড বিভক্ত হয়
আবার কেন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের হইলোরে উদয়?
সেই সব কথা বাদ রাখিয়া আটচল্লিশে যাই চলিয়া
জিন্নাহ সাহেব আসিয়া ঢাকায়
রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে প্রকাশ করেন বক্তৃতায়
সাথে সাথে বঙ্গজাতি শ্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানায়।
সেই থেকে চার বছর ধরে বাঙালি আন্দোলন করে
বায়ান্নতে নাজিম উদ্দিন কয়
রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বাংলাটাংলা কিছুই নয়
তাই শুনিয়া চার ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটে ঢাকা অচল ডাকে
পুরো প্রদেশ অচল হয়ে যায়
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ আট ফাল্গুন ছিল বাংলায়
সেদিন সরকার কার্ফ্যু দিয়ে মায়ের ভাষায় কবর দিতে চায়।
জাতি সেদিন দেয় ঘোষণা এমন আশা আর পোষণা
বাংলা ভাষা হবে না দমন
চুপসে তো যাবে না জাতি আসুক না যতোই সমন
ভাষার দাবির মিছিল নিয়ে করে জাতি রাজপথে গমন।
একশত চুয়াল্লিশ ধারা কার্ফ্যু ভেঙে পথে তারা
ক্যাম্পাসে আর রাজপথে ঢাকায়
ছাত্র যুবক মিছিল করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়
পরিষদ ভবনের দিকে ভাষার মিছিল নিয়ে তারা যায়।
চতুর্দিকে পুলিশ ছিল ক্যাদানে গ্যাস ছেড়ে ছিল
তবু মিছিল সেই পথেই ধায়।
উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে পুলিশরা গুলি চালায়
কতো যুবক লাশ হইল পিছঢালা পথ রক্ত ভেসে যায়।
কতো লাশ যে গুম হইল সেই হিসাব না পাওয়া গেল
রবকত, সালাম, রফিক আর জব্বার
সতেরো জনের লাশ পাওয়া যায় আহত পাঁচজন আবার
হাসপাতালে ক্রমে ক্রমে চিরতরে যায়রে পরপার।
মুক্তি পেলো বাংলা ভাষা পূর্ণ হলো জাতির আশা
ভাষার লড়াই স্মৃতি হয়ে রয়।
বায়ান্নের একুশ ফেব্রুয়ারি ইতিহাসে লেখা হয়
যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক ভাটকবিতা রচিত হলেও অনেক কবিতা সংরক্ষন করা হয়নি। রচয়িতা প্রকাশ করারও তাগিদ অনুভব করেননি। রচয়িতা স্থানীয় জন সাধারনের সামনে পড়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাই গ্রামবাংলার অনেক প্রতিভাবান কবির রচনাবলী তাদের মৃত্যুর পর সমাজের স্মৃতিপট থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। গিয়াসুদ্দিন তেমনি এমন একজন বিস্মৃত লোককবি ভাটকবি। যার উদাত্ত কন্ঠের কবিতা ও গান এককালে গ্রামীন সাধারণ মানুষের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার জন্ম নরসিংদীর নোয়াদির গ্রামে। মৃত্যুবরণ করেন ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে। তার বাবা হিরা মিয়াও ছিলেন বিখ্যাত ভাটকবি। কালের ঘুণাবর্তে তার কবিতা ও গান অধুনা ও সম্পূর্ণ লুপ্ত। পিতা পুত্র দুজনে হাটবাজারে গানের জলসা দিয়ে কবিরাজী ঔষধ বিক্রি করতেন। উভয়েই ছিলেন সুকন্ঠ গায়ক ও কাব্য প্রতিভার অধিকারী। সামান্য লেখাপড়া জানা এ কবি অনেকগুলো ভাটকবিতা রচনা করলেও সেসব মুদ্রিত হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তার রচিত ‘সোনার বাংলা করিলে শ্মশান, এই ভট্ট সঙ্গীতটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত এই ভাট সংগীতটি উল্লেখ করা হলো-
সোনার বাংলা করিলে শ্মশান ওরে জল্লাদ বেঈমান
ভাইরে ভাই – ইয়াহিয়া ইলেকশন দিল বঙ্গবন্ধু পাশ করিল।
খান সেনারা দেখে ভেবে – গেল তাদের মান
সোনার বাংলা করিলে শ্মশান ওরে জল্লাদ বেঈমান।
কারণ বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হলে পাঞ্চাব যাবে রসাতলে
বাংলাদেশের খান সেনাদের চলবেনা শাসনরে
ওরে জল্লাদ বেঈমান সোনার বাংলা করিলে শ্মশান।
ভাইরে ভাই- কাইয়ুম ভুট্টু যুক্তি করে বলছে যাই এহিয়ারে
আপসের বাহানা তরে ঢাকায় চলে যান।
বঙ্গবন্ধু না মানিলে গ্রেপ্তার করব ছলে বলে
ওরে জল্লাদ বেঈমান সোনার বাংলা করিলে শ্মশান।
ভাইরে ভাই- আপসে মীমাংসার তরে এহিয়া আসে ডাকে তারে
এসম্লি কল করিল শোনেন বন্ধুগণ।
এগার দিন মিটিং করে টিক্কা সাজায় সেনাদেরে
হঠাৎ একদিন এহিয়া খান ঢাকা ছেড়ে যান।
ওরে জল্লাদ বেঈমান সোনার বাংলা করিলে শ্মশান।
ভাইরে ভাই- পঁচিশে রাতে পরে হানা দিল শহর জুড়ে
সারা বাংলা দখল করল দারুণ ঢিক্কা খান।
রোকেয়া হল পিলখানা রাজারবাগ পুলিশ থানা
ইকবাল হল বাকী রইল না, চালায় অভিযান।
ওরে জল্লাদ বেঈমান সোনার বাংলা করিলে শ্মশান।
ভাইরে ভাই- বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পিন্ডির পরে
গুলি করে মানুষ মারে কাতারে কাতারে।
ওরে জল্লাদ বেঈমান সোনার বাংলা শরিলে শ্মশান।
ভাইরে ভাই- বাংলার মত দামান ছেলে হাতে অস্ত্র নিল তুলে
ভারতমাতা সদয় হয়ে আশ্রয় করে দেন।
ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিসেনা বাংলার বুকে দিল হানা
খান সেনার ক‚ল পায়না ভেবে অফুরান।
ভাইরে ভাই- ভারত মাতা সদয় হৈয়া মিত্র বাহিনী দেয় পাঠাইয়া
ষোলই ডিসেম্বরে স্বাধীন হৈয়া যায়।
নিয়াজী খান কিবা করে অস্ত্র দিল অরুরারে
বন্দী হৈল খান সেনারা শুনেন বন্ধুগণ
ওরে জল্লাদ বৈঈমান ধ্বংস হয়ে গেল তোদের সাধের পাকিস্তান।
[সোনার বাংলা করিলে শ্মশান/ গিয়াসুদ্দিন ]
১৫ আগস্টে শোক দিবসের কবিতা-
শোনেন ভাই রে ভাই-২ বলে যাই বঙ্গবন্ধুর কথা
একাত্তরে যার কারণে পেলাম স্বাধীনতা।
বঙ্গবন্ধু তিনি-২ সবাই চিনে চিনে না কেই নাই
এই আমাদের বাংলাদেশটি যার খাতিরে পাই।
তিনি জাতির নেতা-২ জাতির পিতা স্থপতি বাংলার
সর্বযুগের সর্বসেরা বাঙালি আমরার।
এই যে আগস্ট মাস-২ সর্বনাশ করছে ঘাতক দলে
এই মাসের পনেরো তারিখ শোক দিবস হয় ফলে।
খতমে কোরান পড়াই-২ মিলাদ পড়াই সিন্নি-সালাদ করে
মাগফেরাত কামনা করি সূরা কেরাত পড়ে।
সেদিন গভীর রাতে -২ এই ঢাকাতে ধানমন্ডিতে হায়
বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে কী ঝড় বয়ে যায়।
আছে ইতিহাসে-২ আগস্ট মাসে কী যে হয় ঘটনা
ইতিহাসে লেখা আছে একটু নয় রটনা।
কিছু সৈন্য সেনা-২ পথ চিনে না বিপথগামী লোকে
জাতির হৃদয় ক্ষত করে দেয় ভাসিয়ে শোকে।
মেজর হুদা, রাশদ-২ নাজমুল, মাজেদ, আজিজ পাশা আর
মেজর ডালিম, ফারুক , রশিদ, কিসমত, শাহরিয়ার।
আরো ছিলা যারা-২ সবাই তারা বিদ্রোহ করিয়া
ফায়ার করে যায় এগিয়ে সীমার বেশ ধরিয়া।
গুলির শ্বদ শুন-২ ঠিক তখনই কামাল জেগে ওঠে
অস্ত্র হাতে দ্রুত বেগে বাইরে আসেন ছুটে।
চলছে গুলাগুলি-২ করেন গুলি ওদের লক্ষ্য করে
মেজর হুদার গুলি লেগে কামাল গেলেন মরে।
ঘাতক সামনে চলে-২ ফায়ার চলে শব্দ ওঠে ভারী
বঙ্গজাতির প্রিয় নেতা ওঠেন তাড়াতাড়ি।
বিষয় বুঝতে পেরে-২ ত্বরিত করে ফোন করেন বারবার
সেনা প্রধান, শফিউল্লাহ কর্নেল জামিল আর।
(তৎকালীন সেনাপ্রধান কে.এম. শফিউল্লাহ ও গোয়েন্দা প্রধান কর্নেল জামিল)
ঐ দিক সিঁড়ি বেয়ে-২ আসছে ধেয়ে বজলুল হুদার দল
এসে দেখে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অবিচল।
আছেন বঙ্গবন্ধু-২ এক বিন্দু নাই যেন ডর-ভয়
‘বন্দি হইয়া গেছেন আপনি’ বজলুল হুদা কয়।
চলুন মোদের সাথে -২ আছে গাতে যে পোশাক আপনার
মোটেও সময় নাই এখন কাপড় বদলাবার।
মুজিব গর্জন ছেড়ে-২ ধমক মেরে বলেন কথা কিছু
তামাকের পাইপ আনতে গেলে ওরাও যায় পিছু।
পাইপটি নিয়া হাতে-২ তাদের সাথে নামতে থাকেন নিচে
হুদার দলের সবাই আছে বঙ্গবন্ধুর পিছে।
নিচে মেজর নুরে-২ উচ্চ স্বরে ইংরেজিতে বলে
সময় নষ্ট করছ হুদা সময় যাচ্ছে চলে।
শুনেন অন্য সুরে।
পঞ্চপদী ভাটিয়ালী
লাখ বছরে এমন নেতা আর হবে না এ বাংলায়
শোক দিবসের সেই কাহিনী শুনেন ভাই সবায়\
একাত্তরে সোনার বাংলার হাজার হাজার ছেলে
স্বাধীনতা আনল কেড়ে বুকের রক্ত ঢেলে।
শেখ মুজিবুর বঙ্গজাতির ঘুম ভাঙানো নেতা
ভুলে নাই পৃথিবীর মানুষ যার ভাষণের কথা।
এমন কবি এমন নেতা পাব বলো আর কোথায়\ঐ
বাংলাদেশের সাত কোটি লোক যাহার আহ্বানে
দাও কাস্তে আর কোদাল হাতে গিয়াছিল রণে।
সেই সে নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
পঁচাত্তরে ঘাতক দলে কাইড়া নিছে প্রাণ।
বঙ্গবন্ধুর শোকে তখন বঙ্গ নিথর হইয়া যায়\ ঐ
ইতোমধ্যে লঙ্কা কান্ড ঘটেছে দোতলায়
নাসেরসহ কয়েকজনকে লাইনে দাঁড় করায়।
কাইন্দা বলে শেখ নাসিরের মারবা কেন মোরে
একজন বলে চুপ ‘হ’ নাসের মারব না রে তোরে।
এই বলিয়া শেখ নাসেরকে বাথরুমেতে নিয়া যায়\ ঐ
মেঘের মতো গোলাগুলি চলছিল তাল ধরে
নাসেরকে বাথরুমে নিয়া বুকে গুলি করে।
কাতর ধ্বনির সঙ্গে নাসের চায় সে একটু খানি।
পানির বদল হায়রে নাসের ব্রাশ ফায়ারের গুলি খায়\ ঐ
এই দিকে জাতির পিতাকে ঘিরিয়া সকলে
সিঁড়ি বইয়া নিচের দিকে যাইতেছিল চলে ।
মেজর নূরে উচ্চ স্বরে ইংরেজিতে কয়
সময় নষ্ট করছ হুদা সময় বেশি নয়।
ফজলুল হক মনিকে মেরে মুসলেম এলো নিচতলায়\ ঐ
শেখ মুজিবকে দেখে মুসলেম দিল গুলি করে
সিঁড়ির উপর থমকে মুজিব সিঁড়িতে যান পড়ে।
পড়ে যাওয়া দেহের উপর ব্রাশ ফায়ার চলিল
ঐ রাতে মোট আঠারো জন হত্যা হইয়াছিল।
সাত কোটির নয়নের মণির রক্তে সিঁড়ি ভেসে যায় \ ঐ
হায়রে বন্ধু, বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে পড়িয়া
শেষ ঘুমে অচেতন হলেন দুই নয়ন বুজিয়া।
যেই নেতা পড়িলেন ভাইরে সোনার বাংলাদেশ
সপরিবারে নিয়া হইলেন একই রাতে শেষ।
আকাশ আর জমিনের সাথে কাঁপছে আরশে ময়ালার \ ঐ
মুজিব হত্যার খবর যখন ছড়ায় বাংলাদেশে
মা-বোনেরা কেঁদে ওঠে পাগলিনীর বেশে।
যুবক-বুড়ো মুটে-মজুর হাতের কাজ ফেলিয়া
হাউ-মাউ করে কেন্দে ওঠে মাথায় হাত মারিয়া।
আকাশ-বাতাস, বৃক্ষলতা কাঁদছে সারা দুনিয়ায় \ ঐ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নাইরে পৃথিবীতে
সোনার বাংলা অমর হইয়া রহিবে জগতে।
যতদিন পৃথিবী আছে মানব অহংকার
বঙ্গবন্ধুর নাম থাকিবে থাকবে রে বাংলার।
বাংলা মানেই বঙ্গবন্ধু দেশ হলো যার উছিলায় \
এই খানে এই শোকের পুঁথি ইতি করে যাই
সম্পাদকের কবিকারের পরিচিতি লিখিয়া জানাই।
জালাল খান ইউসুফী আমার সিলেটে ঠিকানা
প্রথম পাশা, নিজবুরুঙ্গা, বালাগঞ্জ থানা।
কাব্য, ছড়া, গল্প এবং প্রবন্ধেও কলম যায় \
ভাটকবি দারোগ আলী বিখ্যাত পুথি পাঠক, জারীগান গায়ক এবং এক অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা। জন্ম ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বৃহত্তর ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার সাহাপুর গ্রামে। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে তিনি রচনা করেছিলেন ‘বঙ্গবিষাদ পুথি’। এই পুথি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ গ্রন্থিত হলো। পৃথিবীর এ যাবৎকালের সবচেয়ে মুক্তিকামী মানুষকে উন্মাতাল করেছিল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল মুক্তির অন্বেষার। ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকন্ঠে ঘোষণা
ঢাকায় আসিয়াছিল এহিয়া শয়তান
তার সাথে, দৌলতানা আর কায়ুম খান।।
পরিষদ বাতেল করে করিয়া চালাকি
বঙ্গবাসী বুঝে দেলে সবাই তার ফাঁকি।।
ধীরে ধীরে গুজারিয়া গেল তিন মাস
মাওরাদলের চিন্তা শুধু বাংলার সর্বনাশ ।।
মার্চ মাসের তিন তারিখে সর্দার ইয়াহিয়া
বেতার মারফতে আবার দিল জানাইয়া।।
ছয় দফার দাবী ছাড় শেখ মজিবর
ক্ষমতা বকসিব আমি তোমার উপর।।
প্রধান উজির হও তুমি গদিনশীল হইয়া
ছয় দফা এগার দফা সব দিবা ছাড়িয়া।।
এত শুনি বঙ্গবন্ধু বলে এহিয়ারে
এই সব প্রলাপের কথা না বল আমারে।।
শেখ মজিব বলে শুন্ মাত্তরা হারামজাদা
দেশের জনগনে আমি দিয়াছি ওয়াদা।।
ওয়াদার খেলাপ আমি করিতে না পারিব
দফার দাবী দাওয়া কভু নাহিক ছাড়িব।।
এই রাত শুনি গিধি বাহানা জুড়িল
ফের ঢাকায় আসিবার তারিখ করিল।।
তার সাথে আসতে রাজী হইল ভুট্টো চোরা
বড় কথা বলে কাজের বেলায় থোড়া।
ধুয়া:
বঙ্গবন্ধুর ডাক পড়েছে শুনরে পাতি কান
জয় বাংলা জয় বাংলা বলে উড়াও হে নিশান।।
হেথায় মুজিব মাওরাদলের বাহানা দেখিয়া
রমনার মাঠে বাঙ্গালীদের আনিল ডাকিয়া।।
বজ্রকন্ঠে বঙ্গবন্ধু বলে সবাকারে
শুন যত বঙ্গবাসী বলি তোমাদেরে।।
খানের দলে মোদের সাথে করছে টালবাহানা
জনগনের অধিকার সহজে দিবে না।।
অসহযোগ আন্দোলন কর আজ হইতে
দেখিব ক্ষমতায় কিসে থাকে মাওরাজাতে।।
আমি যাহা বলি তাহা মানিবে তাবৎ
মাওরা গোষ্ঠি তাড়াইতে করহ শপথ।।
খাজনা টেক্স যত আছে কিছু নাহি দিবে
মিলের শ্রমিক কেহ কাজে নাহি যাবে।।
দেশের যত চাকুরীয়া চাকরী ছেড়ে দাও
খানের দলের বিরুদ্ধে সব রুখিয়া দাঁড়াও।।
স্কুল কলেজ যত আছে সব বন্ধ দিয়া
সব মিলে যাও তোমরা সংগ্রাম করিয়া।।
বাংলাদেশে আছে যত শহর গেরাম
এক সমানে চালাও সবে জোরেতে সংগ্রাম।।
এবারের সংগ্রাম জেনো মুক্তির সংগ্রাম।
স্বাধীন করিব এবার বাংলা তামাম।।
আরও বলি শুন সবে রাখিবেক মনে।
আমি যদি নাহি থাকি তোমাদের সনে।।
তবে না ডরিবে কেহ পশ্চিমার ভয়ে ।
হাতের কাছে যাহা পাও দাঁড়াবে তা লয়ে।।
আজ হতে এক সমানে সংগ্রাম চালাও।
জয় বাংলা বলিয়া জাতির নিশান উড়াও।।
এত শুনি শপথ করে ছাত্রনেতাগণ।
নূরে আলম সিদ্দিক আর কুদ্দুছ মাখন।।
জয় ধ্বনী করে সবে যত লোকজন।
জয় বাংলা জয় বাংলা বলে কাঁপবে গগন।।
স্বাধীন বাংলা বলে মজিব করিল ঘোষণা।
আল−াতালা পুরাইবে মনের বাসনা।।
বঙ্গবাসী এক তালেতে চালাইল সংগ্রাম।
শহর বন্দর বাজার বস্তি গেরাম।।
[১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকন্ঠে ঘোষণা/ দারোগ আলী]
মূলত: বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙ্গালীর মুক্তির ডাক। এরকম বলিষ্ট কন্ঠস্বর আর মুক্তিকামী মানুষের জন্য স্বাধীনতার ডাক ও নির্দেশনা বিশ্বের আর কোন নেতার ভাষণে শুনা যায়নি। এদেশের মানুষের বুক ভরে গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে যা দেখে যা শুনে পৃথিবীর অপর প্রান্তের মানুষও উদ্দেলিত হয় আলোড়িত হয়। ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়েছে একমাত্র বাঙ্গালী জাতি। বাঙ্গালি জাতিসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে ভাষান্দোলনের শহীদ মিনার। আর বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা শব্দটিরও জন্ম হয়েছে সেই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ থেকে। এদেশের ভাটকবিরাও সেই সময়ের ইতিহাস তুলে ধরতে ভুল করেনি তাদের রচিত ভাটকবিতায়।
একাত্তুরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রচিত হয়েছিল সংগ্রামী লাচারী গান। যে গান গুলো ভাটকবিতার পর্যায়ভুক্ত। আর এসব লাচারীগানের একজন অন্যতম পুরোধা ছিলেন যামিনী কুমার দেবনাথ। জনসাধারণ্যে তিনি ‘যামিনী সাধু’ নামে পরিচিত। তার প্রকৃত পরিচয় মরমি সঙ্গীত ও সাধক রূপে। তিনি ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার সরাইল উপজেলার কালীকচ্ছ গ্রামে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২২ মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিদানচন্দ্র দেবনাথ, মাতা জয়কুমারী দেবনাথ। নিজ গ্রামের পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেই তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার রচিত মরমি গানের সংখ্যা চার হাজারের মতো।
মুক্তিযুদ্ধের সময় কবি স্ত্রীপুুত্র নিয়ে ভারতে চলে যান। তিনি সেখানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বৃদ্ধা মা ও অল্পবয়সী পুত্রকন্যাদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তিনি লেখনীর মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ইচ্ছা করলেন। ১৯৭১ স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ইতিহাসে কথা ও সংগ্রামী গান শীর্ষক পান্ডুলিপিতে কবি যামিনী কুমার দেবনাথ লিখেছেন-
‘জয় বাংলার হত্যাকান্ড আট পৃষ্ঠার কবিতা আমি নিজে গানের সুরে গামে গঞ্জে শহরে শহরে প্রচার করিতে লাগিলাম, তার সঙ্গে অনেক সংগ্রামী গানও গাইতে লাগিলাম গানের মাধ্যমে মুক্তি বাহিনীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করিতে লাগিলাম। শুধু সংগ্রামী গান আর জয় বাংলা হত্যাকান্ড কবিতা দশ থেকে পনর হাজার কপি হইয়া গেল। পাকিস্তানের বর্বরতা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া দিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কেনেডি ত্রিপুরা তুলাবাগান শরনার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনিকে নিজ হাতে জয়বাংলা হত্যাকান্ড কবিতা দিয়ে দিলাম। যেন পাকিস্তানীদের অত্যাচার বিশ্ববাসী জানিতে পারে। তখন পাগলের মত সংগ্রামী গান লিখিয়া, নিজ কন্ঠে প্রচার করিতে লাগিলাম। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তুলাবাগান ক্যাম্পে এসেছিলেন, আমি সে বিশাল সভায় কয়েক দফা চেকিংয়ের পর মঞ্চে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিজ হাতে জয় বাংলার হত্যাকান্ড কবিতা ও একটি অভিনন্দন কবিতা দিলাম। পাকিস্তানী হানাদারদের চরম অবিচার, অত্যাচার নারী নির্যাতন, গণহত্যা সকলের জানার জন্য।’
এখানে ‘১৯৭১/সংগ্রামী লাচারী গান’ কবিতাটি উদ্ধৃত করা হলো-
তেরশ সাতাত্তর বাংলা চৈত্রমাসে দিল হামলা
সঙ্গে নিয়ে বারদ গোলা ঢাকার শহরে।
গোলাগুলি করে ঢাকায়, কত লোকে প্রাণ হারায়
টিক্কা খানে মানুষ মারে ইয়ার ছলনায়।
রাত্র দিবা গুলি ছাড়ে, দালান কোঠা চুরমার করে
দুধের শিশু প্রাণে মারে, জঙ্গী সরকারে।।
তাঁতিবাজার গোয়ালনগর, না পাওয়া যায় লোকের খবর
রাত্র হামলা রাজার বাগে পুলিশের উপর।
লালবাগ শাখারীবাজার, ছিন্ন ভিন্ন নাই তাহার
নরনারী করে সংহার, টিক্কার অর্ডারে।।
ঢাকায় যত থানা ছিল, পাঞ্জাবি দখল করিল
গোলা বারুদ বন্দুক সকল, সব নিয়ে গেল।
মেডিকেল কলেজে গেল, বুলেট দিয়া ছাত্র মারল
অবশেষে প্রাণ হারাইল, সকল ডাক্তারে।।
যে সব কান্ড হয় ঢাকাতে, না পারি মুখে বলিতে
লক্ষ লোকে প্রাণ হারাইল, পাঞ্জাবির গুলিতে।
ঢাকার শহর রক্ত¯্রােতে, ভেসে যায় বুড়িগঙ্গাতে
শহরে নাই লোক বলিতে, টুকাইয়া মারে।।
ছাত্র নেতা শিক্ষক মারে, যত ইতি পায় শহরে
খায়ের উদ্দিন মজা করে, হারিকেনের জোরে।
তার বাবা পাঞ্জাবির দলেরে, ঢাকায় যত খবর করে
তালাস করে ঘরে ঘরে, যত বাঙ্গালী মারে।।
রমনা কালীবাড়ী ঢাকায়, চিহ্ন নাহি পাওয়া যায়
মসজিদ মাজার ছিল সেথায়, গুলিতে উড়ায়।
জগন্নাথ কলেজের উপর, চালাইল ট্রেং মর্টার
ইডেন কলেজ করে চুরমার, সব ছাত্রী মারে।।
চিটাগাং কর্ণফুলিতে, তিনটি জাহাজ লঙ্গর করে
মুক্তিফৌজে গুলি ছাড়ে, উঠতে না পারে।
কামান দিয়া গুলি করে, পেট্রোল পাম্পে আগুন ধরে
সকল টাউন পুড়াইয়া মারে, জঙ্গী সরকারে।
শাসক গোষ্টির জারজ সন্তান, ফগা চদ্রী নাম ধরে
চিটাগাংয়ের জঙ্গীর দালাল, বানায় ফগারে।
ফগা চন্দ্রী বগার মত, ধ্যানে মগ্ন অবিরত
চিটাগাঙ্গের খবর যত, দেয় তার বাবা চাচারে।।
নরসিংদী ভৈরব বাজারে, বিমান লইয়া ঘুরে ফিরে,
বিমান থেকে গুলি ছাড়ে, কত লোক মরে।
প্রথম বোমা বর্ষণ করে, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া শহরে
দ্বিতীয়তে নাপাম বোমায় নরসিংদী পুড়ে।।
বাবা শাহজালাল দরগা ছিল সিলেট সদর টাউনে
ছিন্ন ভিন্ন না রাখিল মেশিনগানে।
কত পীর কামেল ফকিরে, কপালে হাত হায় হায় করে
কত লোকজন প্রাণে মারে, দরগার ভিতরে।।
সিলেট জেলার অন্তর্গত মাধবপুর থানা ধরে
আলোয়াপাড়া গোপালপুর গ্রাম দুই তিনবার পুড়ে।
দালাল গোষ্ঠী লুটপাট করে, রাজাকার মানুষ মারে
যুবা নারী আনে ধরে, কত অত্যাচার করে।
হিন্দু ধর্মের মহাতীর্থ সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ
পাঞ্জাবিরা বোমা ফেলে করলো ধুলিসাত।
যত ধর্মের স্থানে, ধ্বংস করে ইয়া খানে
নিরবিচারে মানুষ মারে, বাঙ্গালী ভাইয়েরে।।
শুন বলি ইয়া সরকার, যত হত্যা কর এবার
জীবন দিয়া আদায় করবো, বাংলার সর্ব অধিকার।
রাজাকারে লুটপাট করে পাঞ্জাবি দেয় পাহারা
ঘরের চালের টিন খুলিয়া নেয় দরজা বেড়া।
ঘরের ভিটির মাটি খুঁড়ে, মুসলিম লীগে ছালা ভরে
ধরে জনে সংহার করে, সুখের সংসারে।
সাহবাজপুরের নুরুল আমিন তোর জন্মের ঠিকানা নাই
কাজে বুঝি গাধার জন্ম, আমি তোমায় বলে যাই।
কি বলিয়া কি করিলে, কত মীরজাফরী করলে
কত ছাত্র শিক্ষক মারলে, বাংলাদেশের ভিতরে
সোনার বাংলা করে শ্মশান, পাকিস্তান জঙ্গী সরকার
কি অপরাধ বাংলার নেতা, ছাত্রছাত্রী শিশুরার।
তোমার দেয়া অধিকারে, শেখ মুজিব ভাই পাশ করে
রাষ্ট্রদ্রোহী কর তারে, নেও পাকিস্তান কারাগারে
সোনার বাংলার নয়নমনি, বঙ্গবন্ধু দেশে নাই
এই সুযোগে সোনার বাংলা পুইড়া করলে ভষ্ম ছাই
জঙ্গী সরকার তোরে জানাই, আর বেশী দিন সময় নাই
আসবে ফিরে শেখ মুজিব ভাই জয় বাংলার ভিতরে।।
ইয়াহিয়া তোরে বলি পাকিস্তান জঙ্গী সরকার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও, বলি বারে বার।
জান না কি বিষধর সাপ, জানলে করবে বাপরে বাপ
তোর কপালে কি মহাপাপ, জানবে কতদিন পরে।।
ইয়া শয়তান তোরে বলি টিক্কারে যাও বলিয়া
ভূট্টো শয়তান ফাঁদ পাতিল দুই শয়তানের লাগিয়া
একদিন বাংলা স্বাধীন হবে, শেখ মুজিব ভাই বাংলায় আসবে।
পাগল যামিনী কয় যাবো সবে, বাংলা মায়ের উদরে।
[১৯৭১ সংগ্রামী লাচারী গান/ যামিনী কুমার দেবনাথ]
(চার)
মুক্তিযুদ্ধের পথুয়া কবিতা/ভাটকবিতায় ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে উঠছে প্রবল ভাবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল কালোরাত থেকে বাংলাদেশ জ্বলছে দাউদাউ করে। সমগ্র দেশ যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের দুঃস্বপ্নে প্রোথিত- গ্রাম বাংলায় ভাটকবিতায় এর স্বরূপ ফুটে উঠে সত্য হিসেবে। ফলে বাংলাদেশের ভাটকবিতায় মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক পংক্তিমালায় দেশ ও সমাজের অঙ্গিকার সোচ্চার হয়েছে জোড়ালো ভাবে সর্বত্র দেশের আনাচে কানাচে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশপ্রেম এবং মানবতাবাদী আবেগের স্ফুরন ঘটেছিল তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভাটকবিরা সেদিন সোচ্চার ছিলেন। তারা তাদের পথুয়া কবিতা/ভাটকবিতায় অবরুদ্ধ দেশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন আবেগের উচ্চারণ রয়েছে ভাটকবিতায়।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে। গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙ্গালীর তৎকালীন প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও ক‚টনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন আনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
অত:পর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যদুস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙ্গালী জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।
তথ্য নির্দেশ:
১. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৫, পৃষ্ঠা-৩৬৭Ñ৩৬৮।
২. শামসুজ্জামান খান ও ড. মোমেন চৌধুরী, বাংলাদেশের ফোকলোর রচনাপঞ্জি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩৯।
৩. আসাদ চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোক সাহিত্য সংকলন-২৯ (ভাটকবিতা), বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৬৩।
৪. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীহট্টের ভট্টসঙ্গীত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা, কলিকাতা, ১৯৮৯।
৫. নন্দলাল শর্মা, ফোকলোর চর্চায় সিলেট, বাংলা একাডেমী , ১৯৯৯ , পৃষ্ঠা-১১।
৬. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীহট্টের ভট্টসঙ্গীত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা, কলিকাতা, ১৯৮৯।
৭. আসাদ চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোক সাহিত্য সংকলন-২৯ (ভাটকবিতা), বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠাÑ২৭২।
৮. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, পৃষ্ঠা-১৩।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. আসাদ চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোক সাহিত্য সংকলন-২৯ (ভাটকবিতা), বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৭৬।
১১. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, পৃষ্টা-১৩।
১২. আসাদ চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোক সাহিত্য সংকলন-২৯ (ভাটকবিতা), বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৯৬।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. আসাদ চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত লোক সাহিত্য সংকলন-২৯ (ভাটকবিতা), বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৯।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩
১৮. হাসান ইকবাল, ভাটকবিতায় নারী (প্রবন্ধ), সাহিত্য সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা- শব্দঘর, মোহিত কামাল সম্পাদিত, নভেম্বর ২০১৪, ঢাকা।
১৯. বিলু কবীর, হাটুরে কবিতায় সমাজ, ২০১২, ঢাকা।
২০. জালাল খান ইউসুফী, বাংলাদেশের পুঁথিকাব্য, ২০১৭, পৃষ্ঠা―১২।
২১. মুনতাসীর মামুন, পূর্ববঙ্গের বিচিত্র সব বই, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১
২২. মুনতাসীর মামুন, ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বইয়ের খোঁজে, ২০০৬, ঢাকা।
২৩. মামুন তরফদার, টাঙ্গাইলের লোক ঐতিহ্য, ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬, ঢাকা।
২৪. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, ঢাকা।
২৫. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, ঢাকা।
২৬. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান,, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা―১৬৩।
২৭. জালাল খান ইউসুফী, বাংলাদেশের পুঁথিকাব্য, ২০১৭, পৃষ্ঠা―১৭৭।
২৮. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান,, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা―১৯৪।
২৯. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান,, বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা, ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা―৩০১।