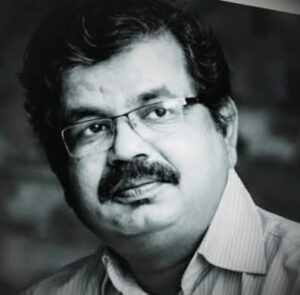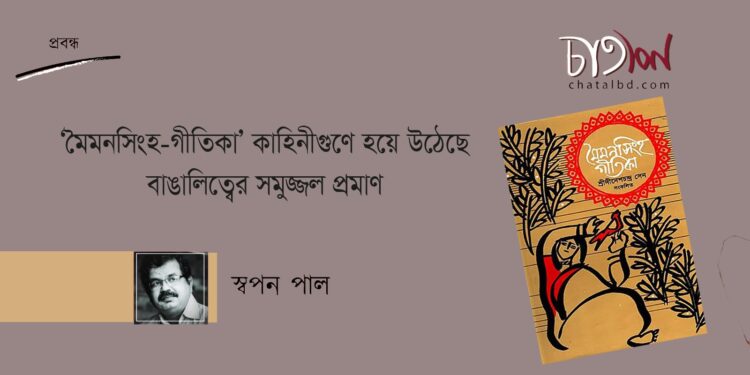আলোচনার সূত্রপাত
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগানের একটি সংকলন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে চন্দ্রকুমার দে প্রচলিত এ পালাগানগুলো সংগ্রহ করেন ও ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে মৈমনসিংহ গীতিকা নামে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি বিষয়মাহাত্ম্যে ও শিল্পগুণে শিক্ষিত ও সাহিত্যবোদ্ধা মানুষের মন জয় করে।
প্রাচীনকাল থেকে পূর্ব—ময়মনসিংহে সংস্কৃতি চ”র্ার একটা ঐতিহ্যধারা অব্যাহত ছিল। এর উজ্জ্বল এক উদাহরণ ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। এতে আঞ্চলিক জীবনধারার একটা নিখুঁত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। পালাগানের অধিকাংশই ছিল পূর্ব—ময়মনসিংহের কোন না কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত। শুধু তাই নয়, অসমতল পাবর্ত্যাঞ্চল, নিবিড় বন, বিস্তৃত হিল্লোলিত হাওড়—বিল, খরগ্রোতা ও স্রোতস্বিনী নদী, পশুপক্ষী, পালতোলা নৌকা প্রভৃতি ছিল পালাগুলোর বিচরণক্ষেত্র এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা গীতিকাকে করে তুলেছে অতুলনীয় এবং আকর্ষণীয়।
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ পূর্ব—ময়মনসিংহের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত ফল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র প্রথম ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হলে দেশে—বিদেশে এটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এর ইংরাজী—সংস্করণের মহুয়া পাঠ করে অস্ট্রিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পকলা ও ইতিহাসবিদ ড. স্টেলা ক্র্যামরিচ ডঃ সেনকে লিখেছিলেন ‘সাতদিন জ্বরের ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মত দেখিয়াছি। আমি ভারতীয় সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মম্মর্স্পর্শী এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই।’ ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনও মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন— ‘আপনি এই পরম উপাদেয় জিনিসগুলি শুধু পূর্ববঙ্গে নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন।’ ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ড. সিলভ্যান লেভি লিখেছিলেন, ‘ফরাসি দেশের শীতপ্রধান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এই সকল গল্প পড়বার সময়ে মনে হয়েছে চিরবসন্তের রাজ্যে বিহার করছি’ এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ শিল্পী রোদেনস্টাইন বলেছিলেন, ‘অজন্তা ও অমরাবতীর যে সকল অপূর্ব রমণীমূর্তি দেখেছি, এই সকল গল্পের নায়িকারা যেন সেই রমণীদেরই জীবন্ত লেখমালা।’
ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় দীনেশ চন্দ্র সেন তৎকালীন লর্ড রোনাল্ডসকে ‘দু’ছত্র’ লেখার অনুরোধ করলে তিনি লিখেছিলেন— ‘এই পালাগুলি এত চমৎকার যে, দুটি ছত্র লিখিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি না।’ প্রকাশের পর এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনোভাব কেমন হয়েছিল, সে সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন— ‘তাঁহার সমস্ত প্রাণভরা সন্তোষের হাসিতে স্বীয় গুম্ফ পর্যন্ত উজ্জ্বল ও অলংকৃত করিয়া আমার দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন, পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে— পুন্নমাসীর চাঁদ যেমন দেখায় নদীর তলা!’
বাংলার এই অমূল্য সম্পদ গীতিকাগুলো বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি হয়েছিল বলেই ডঃ দীনেশ সেন রোম্যঁা—রোলাঁ, লর্ড রোনাল্ডসে, নিবেদিতা প্রমুখ বিদেশী মনীষিদের বহু প্রশংসা পেয়েছেন। সিষ্টার নিবেদিতার ভাষায় বলা যায়—‘বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। … তাহাদের মেঠো সুরে রাগিনী না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাহাদের কুঁড়ে ঘরে সোনা—রূপার থাম না থাকিলেও আঙ্গিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।’
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ‘জাভা—যাত্রীর পত্র’—এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘ময়মনসিংহ থেকে যে সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সুর। কোন শহরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ—দুঃখের প্রেরণায় লেখা এই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবুও এ ভিড় বিশেষকালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে, তবুও তা বিশ্বেরই ফসল তা ধানের মঞ্জুরী।’
গাথাগুলি নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্ত মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য জায়গা করে নিয়েছে
ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ‘বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির’ অন্তর্ভুক্ত ময়মনসিংহ ছিল বড় জেলাগুলির একটি। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে তখন ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে ছিল গারো পাহাড়, দক্ষিণ—পূর্বে ছিল জলাকীর্ণ কর্দমাক্ত নিম্নভূমি। ব্রহ্মপুত্র, ধনু, কংশ, সোমেশ^রী, সুতি, নরসুন্দা, ঘোরাউত্রা প্রভৃতি নদনদী প্লাবিত এ অঞ্চল। অঞ্চলটিতে ছিল আদিবাসী ও পাহাড়িদের আনাগোনা। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া এই অঞ্চলের মানুষ খুব বেশি পায়নি। পালাগুলোর অধিকাংশই পূর্ব—ময়মনসিংহের কোন না কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ময়মনসিংহের নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের বাতাসে ভেসে বেড়াত এক বিশেষ ধরনের আখ্যানধর্মী কাব্য,—যেগুলো হয়ে উঠেছিল নরনারীর চিরায়ত প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের মুখে মুখে রচিত এইসব কাহিনীতে গায়েনরা সুর দিয়ে গেয়ে বেড়াত। এর ফলে মুখে মুখেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এইসব গীতিকা। বিশেষতঃ নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্ত মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য জায়গা করে নিয়েছে এই গান বা গাথাগুলি।
পালাগুলো সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, ‘যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ছন্দের—শব্দৈশ্বয্যের্র কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়ত বড় বড় তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল। যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রম্ন কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না।’
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় ১০টি আখ্যান স্থান পেয়েছে, যথাঃ মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ানা মদিনা। ভনিতা থেকে কিছু গীত রচয়িতার নাম জানা যায়, যেমন মহুয়া—দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী— নয়ানচাঁদ ঘোষ, কমলা—দ্বিজ ঈশান, দস্যু কেনারামের পালা— চন্দ্রাবতী, দেওয়ানা মদিনা— মনসুর বয়াতি। কঙ্ক ও লীলার রচয়িতা হিসেবে চার জনের নাম পাওয়া যায়— দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বিনোদ ও নয়ানচাঁদ ঘোষ। অবশিষ্ট গীত রচয়িতাদের নাম জানা যায় না।
নারী চরিত্রের উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ভূমিকায় ভেসে গিয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতার সমাজ—আরোপিত দেয়াল
আখ্যানগুলি লোকসমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। পার্থিব জীবনের কথাই গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দস্যু কেনারামের পালা ছাড়া বাকি ৯টি পালার মুখ্য বিষয় নর—নারীর লৌকিক প্রেম। প্রেমের পরিণতি কোনোটিতে মিলনাত্মক, কোনোটিতে বিয়োগান্তক। বেশিরভাগ পালার নামকরণ করা হয়েছে প্রধান নারী চরিত্রের নামে। যেমন— মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, কাজলরেখা, রূপবতী। এ থেকে অনুমান করা যায়, সেই সময়ে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে নারীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসিত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা সতীদাহ প্রথা বন্ধ কিংবা নারী শিক্ষা চালু করতে তথা সমাজে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নারীকে স্বাধীনভাবে জীবন সঙ্গী বেছে নেবার স্বীকৃতি দিয়েছে—নারীর সুখ দুঃখকে প্রাধান্য দিয়েছে।
গীতিকাগুলোর কাহিনীতে নারী চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। এইসব নারী চরিত্রের মূল আদর্শ হল একনিষ্ঠ প্রেম। নারীদের একনিষ্ঠ প্রেম ও বলিষ্ঠ চরিত্র থেকে কেউ কেউ মনে করেন, গীতিকাগুলিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থাকতে পারে। ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে অভিভাবকের অভিমতের বিরুদ্ধে গিয়ে জীবনসঙ্গী বেছে নেবার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে—এমন বাস্তবতায় ভরা এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে গানগুলিতে। প্রেমের প্রতিষ্ঠায় নারীরাই সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছে বেশি। আর সেই প্রেমেই ভেসে গিয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতা ও জাত্যভিমানের সমাজ—আরোপিত দেয়াল। এইসব নারী—চরিত্র সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র ভূমিকায় বলেন, ‘এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।’
গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্ম আইনকানুনে এবং আচায্যের্র মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুব্বর্লতার ছদ্মবেশ মাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না।…তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।’
মঙ্গলকাব্য ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী; ময়মনসিংহ গীতিকা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা
রচয়িতাদের আবির্ভাব কাল, কাব্যের জীবনকথা, আর্থ—সামাজিক পটভূমি, ভাষাদর্শ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে গীতিকাগুলি মধ্যযুগে রচিত বলে ধারণা করা হয়। ‘কাজলরেখা’ রূপকথাধর্মী; এর বিষয়বস্তু প্রাচীন। এটি ছাড়া অন্য সব গীতিকায় সামন্ত যুগের সমাজ—মানস ও মূল্যবোধের ছাপ রয়েছে। রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজী, কারকুন, সওদাগর,পীর—দরবেশ, সাধু—সন্ন্যাসী প্রভৃতি চরিত্র মধ্যযুগের মুসলিম শাসন—ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতার স্পর্শরহিত সমাজজীবনের এই ছবি মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভর কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র। সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করেও মানবপ্রেমের মহিমা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং নৈতিকতা ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’কে এমন সাহিত্য মূল্য ও মর্যাদা দান করেছে, যা আধুনিক যুগের উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় বলেই অনেক সাহিত্যবোদ্ধা অভিমত প্রদান করেন ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনেশচন্দ্র সেনকে এক পত্রে লিখেন, ‘বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী ; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্ম—বিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি।’
এগুলিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য ড. দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ইংরাজি অনুবাদ করেন। এর নাম দিলেন— Eastern Bengal Ballads। বিদেশি পণ্ডিতরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে এই আখ্যানমূলক কাব্যগুলিকে ২২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মৈমনসিংহ গীতিকার একজন আধুনিক পাশ্চাত্য গবেষক হলেন ড. দুসান জবাভিতেল। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম— Bengali Folk-Ballads from Mymensingh। রোমাঁ রোলাঁর ভগ্নী মেডেলাইন রোলাঁ Eastern Bengal Ballads—এর ফরাসি অনুবাদ করেন। এছাড়া রোমা রোলাঁ, সিলভাঁ, লেভি, পজিটর, জুল বলখ্ প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁরা দেখিয়েছেন মহুয়াা পালার সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগীয় রোমান্স ‘ইসাল্ট’ ও ‘অক্সাসিন’ এবং ‘নিকোলেটে’র প্রেম কাহিনীর সাদৃশ্য আছে ।
ফরাসী পণ্ডিত রোম্যাঁ রোলাঁ দীনেশচন্দ্র সেনের Eastern Bengal Ballads Mymensingh—এর (১৯২৩) ফরাসি অনুবাদ পাঠ করে বাংলার এই গীতিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, দীনেশচন্দ্র প্রথম ব্যক্তি, যিনি বৃহত্তর নাগরিক সমাজের কাছে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ কিংবা ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’কে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ধারক হিসাবে এই গীতিকা বাঙালির অনন্য জীবনাচরণকে নির্দেশ করে—সে কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। দীনেশচন্দ্র ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র ভূমিকায় গীতিকাগুলি সংগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করেছেন।
পাশ্চাত্যের ব্যালাডধর্মী রচনা হল গীতিকা। Ballad শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Ballare শব্দ থেকে। এর অর্থ হল নৃত্য। অর্থাৎ নৃত্য গীত মুলক রচনা হল গাথা বা গীতিকা। দীনেশ চন্দ্র সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য Ballad শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে গীতিকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গীতিকার চারটি উপাদান —ক্রিয়া, চরিত্র, উপস্থাপন, বিষয়।
‘মালীর যোগান’দার চন্দ্র কুমার দে এবং ‘মালাকার’ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ কিংবা ‘পূব্বর্বঙ্গ গীতিকা’ আমাদের পরিচয়, আমাদের সম্পদ। যে সম্পদ খুঁজে পেতে একজন চন্দ্র কুমার দে’র কেটে গিয়েছে পুরো এক জীবন। দীনেশ চন্দ্র সেন জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তার শ্রী বৃদ্ধি করেছেন।
কয়েকশো বছর ধরে ময়মনসিংহের গ্রামে—গঞ্জে মানুষের সুরে—গল্পে ভেসে থাকা এই গাথাগুলোকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সন্তান চন্দ্র কুমার দে কলমবন্দী করেন এবং তিনি তা বাংলার তথা কলকাতার শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। চন্দ্র কুমার দে (১৮৮৯—১৯৪৬) তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহাকুমার (বর্তমান জেলা) কেন্দুয়া থানার (বর্তমান উপজেলা) আইথর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চন্দ্রকুমার দে’র যতোটা সমাদৃত হওয়ার কথা ছিল, তা তিনি হননি। চন্দ্রকুমার দে কতোটা উপেক্ষিত, তার একটি প্রমাণ হল, উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেয়া তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখটি নিয়ে এখন পর্যন্ত সাহিত্য বোদ্ধারা নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। যখন তাঁর নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা হয় ‘১৮৮১—১৯৪৫’, তখন তা অনেক ‘সংশয় ও কিন্তু’র সঙ্গে আপোষ করেই লেখা হয়। এমন উপেক্ষিত চন্দ্রকুমার দে’র জীবনটাও ছিল দুঃখে ভরা। খুব অল্প বয়সেই চন্দ্রকুমার মাতৃহারা হন। কৈশোরে গ্রামের জমিদার তাঁর পিতার সহায়—সম্পত্তি চোখের সামনে কেড়ে নিলে পিতা রামকুমারও অচিরেই শোকে দুঃখে পৃথিবীর মায়া কাটান। অল্প বয়সে মাতা—পিতা হারিয়ে প্রথাগত শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হন তিনি। স্বল্প সংস্কৃত জানতেন। এরপর পেট বাঁচাতে নিজ গ্রামের মুদি দোকানে মাসিক ১ টাকা বেতনের চাকুরী নেন তিনি। কিন্তু ভাবুক এবং সাংসারিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ চন্দ্রকুমারকে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ দোকান থেকে অর্ধচন্দ্র পেতে হয়। এরপর চন্দ্রকুমার কলেরায় আক্রান্ত হন। অভাবের কারণে পরিত্রাণের আশায় হাতুড়ে চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করে সুস্থ তো হলেনই না, উপরন্তু মানসিক বৈকল্য দেখা দিল, যা প্রায় দু’বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই চরম দুর্দিনে স্থানীয় জমিদার তারকনাথ তালুকদারের কাছে কর আদায়ের কাজ পান মাসিক দু’টাকা বেতনে। আরও পরে গৌরীপুরের জমিদারিতে গোমস্তার কাজ পান মাসিক আট টাকা বেতনে। তহশীল আদায় করতে চন্দ্রকুমারকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত। ঐ সময়ই তিনি কৃষক তথা গ্রামের মানুষের কণ্ঠে শুনতে পান অপূর্ব সব পল্লী গাথা ও উপাখ্যান। গানগুলো চন্দ্রকুমারকে এতোটাই মোহিত করে যে, শুনে শুনেই তা তিনি খাতায় লিখে রাখতেন। তিনিই প্রথম এই গান বা আখ্যানকাব্যগুলি সংগ্রহ করে লিখে রাখেন। সেই সময় ময়মনসিংহ থেকে ‘সৌরভ’ নামে একটি উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশিত হত। কেদারনাথ মজুমদার পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। এক সময় চন্দ্রকুমার এই পল্লী গাঁথাগুলোর সৌন্দর্যের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রবল তাগিদ অনুভব করেন। আর সেই কারণেই বিখ্যাত সৌরভ পত্রিকায় এগুলোর উপর লেখা পাঠাতে শুরু করেন। চন্দ্রকুমার দে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রবন্ধ লিখতেন এই পত্রিকায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২০) ‘মালীর যোগান’ নামে লোকসাহিত্যের ওপর লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচলিত কয়েকটি গান কবিতার মতো করে প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি কবি চন্দ্রাবতী বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে পালার কথা উল্লেখ করেন।
এই প্রবন্ধ পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন রিডার এবং সিনেটের সদস্য দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬—১৯৩৯) অত্যন্ত উৎসাহিত হন। বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামের সন্তান ড. দীনেশচন্দ্র সেন লোক এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশের কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরীক্ষকের পদে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরে বাংলা রিডারের পদে যোগ দেন (১৯০৯)। পরের বছর সিনেটের সদস্য হন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ পান। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি লাভ করেন। তিনি চন্দ্রকুমার দে—কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাহকের কাজ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস—চ্যন্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্মতিতে সত্তর টাকা মাসিক বেতন দিয়ে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ময়মনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের আখ্যান কাব্য বা গাথা সংগ্রহ করার কাজে আরও কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয়। কবি জসীমউদ্দীন, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্র চন্দ্র দে, বিজনবিহারী লাল, রজনীকান্ত ভদ্র প্রমুখ ব্যক্তিকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কাজে দীনেশচন্দ্র সেনকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। অবশেষে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে’র সংগ্রহ করা গীতিকাগুলো হাতে পান। এই গীতিকাগুলোর বেশির ভাগই তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সংগৃহীত পালাগুলি থেকে ১০টি পালার ইংরেজি অনুবাদ— Estern Bengali Ballads -mymensingha-part–1 ড. দীনেশ চন্দ্রসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। অন্য পালা গুলি পূর্ববঙ্গ গীতিকা (বধংঃবৎহ ইবহমধষর নধষষধফং) নামে ভিন্ন ৩টি খন্ডে প্রকাশিত হয়। চারটি খন্ডে পালার সংখ্যা যথাক্রমে; ১ম খন্ড—১০, ২য় খন্ড—১৪, ৩য় খন্ড—১১ চতুর্থ খন্ড—১৯; মোট ৫৪টি পালা। প্রথম খন্ডটির নাম ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র ১০টি পালার সংগ্রাহকই চন্দ্রকুমার দে। অন্যান্য খন্ডের সংগ্রাহকদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন—কবি জসীম উদ্দিন, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল রায় প্রমুখ।
দীনেশচন্দ্র সেন তার জগদ্বিখ্যাত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ ও ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’য় তথ্যদাতা হিসেবে চন্দ্রকুমারের পরিচয় সন্নিবেশিত করেছেন, তাঁর জন্যে বিনে পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, অনাথ ও চিররুগ্ন চন্দ্রকুমার যখন স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন দীনেশচন্দ্র তাঁকে চাকুরী—থাকা—খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকুমার কেবল সংগ্রাহকই রয়ে গেছেন, হতে পারেননি মূল নায়ক। চন্দ্রকুমার বিনয়ের সাথে বলেন, ‘দীনেশচন্দ্র আমার সংগৃহীত ভাঙ্গা ইটে আজ বঙ্গ ভাষার বিচিত্র তাজমহল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আমি তাহার মজুর মাত্র। তিনি এ বিরাট যজ্ঞভূমির অধিনায়ক হোতা। আমি শুধু সমিধ কাস্ট বহন করিয়াছি মাত্র।’
আসলেই ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ এক তাজমহল, যার রসে বুঁদ হয়ে থাকেন রোম্যাঁ রোঁলা, জুলে ব্লক, সিলভান লেভি, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি জগৎ প্রসিদ্ধ পন্ডিতগণ। কিন্তু এই তাজমহল গড়ার নায়করূপে যুগে যুগে স্বরিত—পূজিত হন দীনেশচন্দ্র সেনই; দীনেশচন্দে্রর আলোয় জ্বল জ্বল করে বিশ্বসভায় দ্যুতি ছড়িয়ে যায় ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’, অনেকটা সম্রাট সাজাহানের তাজমহলের মত করেই। এদিকে আড়ালে—আবডালে, লোকচক্ষুর একেবারে অন্তরালে থেকে যান তাজমহলের আসল কারিগর হতভাগা চন্দ্রকুমারেরা।
‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র ভ’মিকায় চন্দ্রকুমার দে’র প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, ‘কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবানই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূব্বের্ যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, বিল ও পুষ্করিণীতে পরম ও কুমুদের কুঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলিত—এই সকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ ত্নময় হইয়া যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না। কিন্তু লোকের রুচি এইদিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবারও লোকের অভাব হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্য—কথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি,—নানা গ্রামে পয্যর্টন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতিটি পালা সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।’
চন্দ্রকুমার দে মোট ২১টি পালা সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১০টি ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় গ্রন্থিত হয়েছে। বাকীগুলো দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’য় স্থান পেয়েছে।
মৈমনসিংহ—গীতিকা’র সময়ের রাজনৈতিক—সামাজিক অবস্থা এবং ব্যবস্থা
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব—ময়মনসিংহ গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল। এরপর এই অঞ্চল গুপ্ত—শাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে প্রাগ জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়। কামরূপের শাসনে এ অঞ্চল এক সময়ে হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্দে্র পরিণত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের আহ্বানে চীন—পর্যটক হুয়েনসাঙ্গ এই অঞ্চলে এসেছিলেন। চীন—পর্যটক এখানকার মানুষের চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষার অশেষ প্রশংসা করেছেন। প্রাগ—জ্যোতিষপুরের পতনের পর পূর্ব—ময়মনসিংহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণযোদ্ধা কোচ—রাজবংশীয় বৈশ্য গারো নামক রাজার অধিকৃত সুষঙ্গ দুর্গাপুর রাজ্য কেড়ে নেন। ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুরের গড় জরিপার রাজা দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় করায়ত্ত্ব করেন। সম্ভবতঃ ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মসনদ আলী জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্নণ হাজরাকে পরাজিত করে সেখানে সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে খালিয়াজুড়ি, মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপরাপর রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যগুলি পরিশেষে মুসলমান শাসকগণের অধিকৃত হয়, অথবা ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া মুসলমান শাসকগণের বশ্যতাস্বীকারপূব্বর্ক কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। এর বিবরণ কেদারনাথ মজুমদার ‘মৈমনসিংহের ইতিহাসে’ লিপিবদ্ধ করেছেন।
প্রাগজ্যোতিষপুর এবং মুসলমান শাসকগণের কালের মধ্যবতীর্ সময়ের দুই—তিন শতাব্দী অপর এক রাষ্ট্রীয় শক্তি এই ‘পূব্বর্—মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল’। কিন্তু সেনবংশীয় রাজাগণ পশ্চিম—ময়মনসিংহ অধিকার করলেও বহু বিল সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল ‘পূব্বর্ প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই পূব্বর্—মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ—প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।’ দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেন, ‘প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ— প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দে্র পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূব্বর্—মৈমনসিংহ সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পূব্বের্ কামরূপে যে হিন্দুধম্মের্র আদর্শ ছিল, পূব্বর্—মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। এই হিন্দুধম্মর্ উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কম্মর্বাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূব্বর্ মিশ্রণ ছিল। সেই হিন্দুধম্মের্ বল্লাল সেন—প্রবর্তিত ‘গৌরীদান’, আচারবিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। …সম্ভবতঃ তখনও জাতিভেদ সেই দেশে এরূপ কঠোর হইয়া উঠে নাই । তথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়।…
সুতরাং শত শত আচারবিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইনকানুনে বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুসমাজের যে মূত্তির্ কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাড়া হাতে বর্তমান কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে,—এই পল্লীগাথাবর্ণিত সমাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে ছেলে এক বৎসর বয়স হইতে পূরো পাঁচ বৎসর পয্যর্ন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্যপানপূব্বর্ক চাঁড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, ব্রাহ্মণকুল—তিলক গর্গ নিজের গায়ের পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ দিনে কি তাহা সম্ভবপর হইত ? চাঁড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযমুনার ন্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না।…এই পল্লীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু কখনই নারীধর্ম ত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ নারীধম্মের্র যে জীবন্ত মূত্তির্গুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্নতায়, বিপদে, ধৈয্যের্ উপায়—উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।’
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যে বহু শতাব্দীকাল ধরে পরস্পরের সাথে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বাস করছিল, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র কাহিনীগুলো পাঠে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দীনেশ চন্দ্র সেন এ সম্পর্কে যথার্থভাবেই বলেছেন, ‘দেওয়ান সাহেবদের অত্যাচারের কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ‘মুসলমানী অত্যাচার’ বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় হইবে। এই অত্যাচার দুব্বর্লের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচারীর ব্যভিচার, —ইহার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু—মুসলমানের ধম্মর্ বা জাতিঘটিত কোন ঘটনা নহে। এক দিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজীকে শূলে চড়াইয়া দিতেছেন। এক দিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের মাতুল ব্রাহ্মণকুলগৌরব ভাটুক ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এক দিকে যেরূপ অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা, অপর দিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী পরস্ত্রীলিপ্সু হিন্দুকুলতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নিম্মর্ম মূত্তির্ আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সব্বর্ত্রই ছিল।’
প্রসঙ্গক্রমে দীনেশ চন্দ্র সেন সেই সময়ের আলোকে সুশাসন দুঃশাসনের যে স্বরূপও উল্লেখ করেছেন, তা আমাদেরকে তৎকালীন সামাজিক—রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতার প্রবল—প্রমত্ত রূপের কথাও মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, ‘যদি রাজা ভাল হইতেন, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকিত না। সোণার ডাটা লইয়া রাইয়তের ছেলেরা খেলিতে থাকিত, কলার পাতা বেচিয়া লোকে পাকা বাড়ী তুলিত, ঘাস—বেচা লোকে হাতী কিনিতে সাধ করিত, লোকে ধনকড়ি যেখানে সেখানে শুকাইতে দিত, ধনরত্ন পথে ফেলিয়া রাখিলেও চোরদস্যুর উপদ্রব থাকিত না। আবার রাজা কি মন্ত্রী অত্যাচারী হইলে রাইয়তেরা তাহাদের বলীবদ, লাঙ্গল—জোয়াল এবং ফাল বিক্রয় করিয়াও ত্রাণ পাইত না, অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দুধের ছেলেকে বিক্রয় করিত। বানিয়াচঙ্গের অত্যাচারী দেওয়ান দুলালের কারাগৃহ হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্রূর বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং এই দুব্বর্লের উৎপীড়ন ইতিহাসবিশ্রম্নত সনাতন ঘটনা, হিন্দু বা মুসলমানের নামাঙ্কিত করিয়া ইহা জাতিবিদ্বেষ উস্কাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ করা উচিত নহে। মুসলমান রাজত্বে, মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী ছিল, এইজন্য হয়ত অত্যাচারীর সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশী ছিল,—কিন্তু সে দোষ ক্ষমতার, কোন শ্রেণীবিশেষের নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিকে অত্যাচারী মুসলমান ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে পৈতা—কাড়িয়া লইয়া তাহার মুখে থু থু দিতেছে, অপর দিকে হিন্দু গোপেরা মুসলমান কাজীর দাড়ি উপড়াইয়া তাহার মুখে ছাগের রক্ত মাখিয়া দিতেছে, সুতরাং কেহই কম নহে।’
মৈমনসিংহ—গীতিকা’র ভাষা
‘মৈমনসিংহ—গীতিকা’র ভাষা প্রসঙ্গে গ্রন্থটির ভূমিকায় দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেন, ‘মৈমনসিংহ—গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বহুশতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর ভাষা।’ তিনি আরও বলেন যে, এখানে কোনো ভেদাভেদ নাই। ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় উর্দু উপাদান ততটাই ঢুকিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে যতোটা এদেশে আসিয়া বাংলা হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেন, ‘এই গীতিসাহিত্য হিন্দু—মুসলমান উভয়ের, এখানে পন্ডিতগণের রক্তচক্ষে শাসাইবার কিছু নাই। লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি, মুসলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, মুসলমান নায়িকা, এবং মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা কবিরা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন’।
লোক—সাহিত্যের ভাষা দিয়ে কাল নির্ণয় করা কঠিন; কারণ অনেক সময় গাথাগুলোর অলিখিত ভাষা মানুষের মুখে মুখে কালেকালে বদলে যেতে পারে। পালাগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে নায়কের নায়িকার বাড়িতে অবস্থান নেয়া এবং পালিয়ে গিয়ে নায়ক—নায়িকার মিলিত হওয়া প্রবণতা দেখে অনেকে অনুমান করেন, এগুলো রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ পূর্ব—ময়মনসিংহের আদিবাসীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রবল—প্রভাব কালে। কারণ পূর্ব—ময়মনসিংহে তথা পূর্ব—বাংলায় আদিবাসীদের মধ্যে বরের বউয়ের বাড়িতে অবস্থান করার প্রথা প্রচলিত আছে।
আপাতত শেষ কথা
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এক সফরে ময়মনসিংহে এসেছিলেন। আঠারোবাড়ির তৎকালীন জমিদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন আঠারোবাড়িতে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রমোদ লাইব্রেরি উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উদ্বোধন করার কথা হলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ’আমার গান দিয়ে শুরু করতে হবে তা কেন, দীনেশচন্দে্রর পালাগান অপূর্ব। মৈমনসিংহ থেকে যে সকল পালা গান সংগ্রহ হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সুর, মানুষের চিরকালের সুখ দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাঁথা। মৈমনসিংহ গীতিকার কাল নির্ণয় চলে না। ওটা আবহমান কালের— যার মধ্যে একটা আশ্চর্য কবিত্ব আছে। আমি এসেছি সেই গান শুনতে, সেই দৃশ্য অবলোকন করতে। মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালা আমার খুব প্রিয়।’
বাংলা ১৩৩৬ সনে (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত ‘সারস্বত সাহিত্য সম্মিলন’—এ চন্দ্রকুমার দে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যার উপসংহারে তিনি বলেন, ‘আমি ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক। আমি হীন নহি—উপেক্ষিত নহি—ইহার চাইতে গর্ব গৌরব করিবার জিনিস আমার কিছুই নাই। আমার ময়মনসিংহ আজ সমগ্র জগতের মধ্যে তাহার সন্মানের আসন বাছিয়া লইয়াছে।’
চন্দ্রকুমার দে’র কথার সাথে যোগ করে আমরাও বলতে চাই, ‘মৈমনসিংহ—গীতিকা’ যেমন ময়মনসিংহ অঞ্চলকে জগত সভায় সম্মানের আসন দিয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে অনন্য এক মাত্রায়। এর সাথে এও বলতে হবে যে, ‘মৈমনসিংহ—গীতিকা’ কাহিনীগুণে হয়ে উঠেছে বাঙালিত্বের সমুজ্জ্বল প্রমাণ।
সহায়ক গ্রন্থঃ
১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. ময়মনসিংহের ইতিহাস—কেদারনাথ মজুমদার।
৩. ময়মনসিংহের ইতিবৃত্ত—সজলকান্তি দত্ত রায় সম্পাদিত।
৪. মৈমনসিংহ গীতিকা —ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
৫. সেন বাহাদূর দীনেশচন্দ্র সেন—সৈয়দ আজিজুল হক।
৬. চন্দ্রকুমার দে—যতীন সরকার
৭. Estern Bengal Ballads Mymensing – Dinesh Chandra sen, Raibahadur, B.A. D. Llit. Head Examiner and Lecturer of Calcutta University